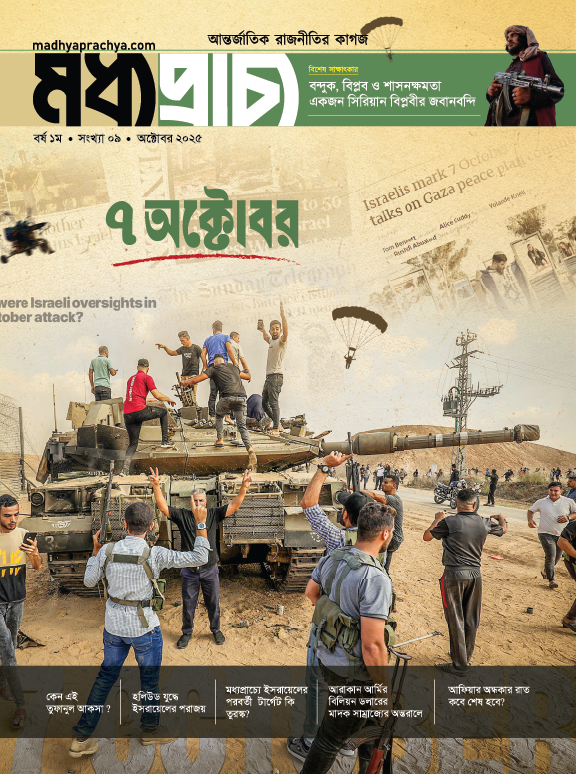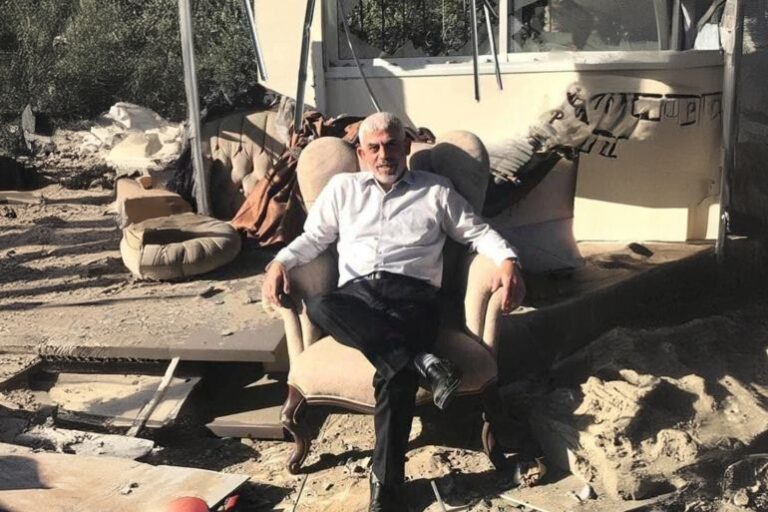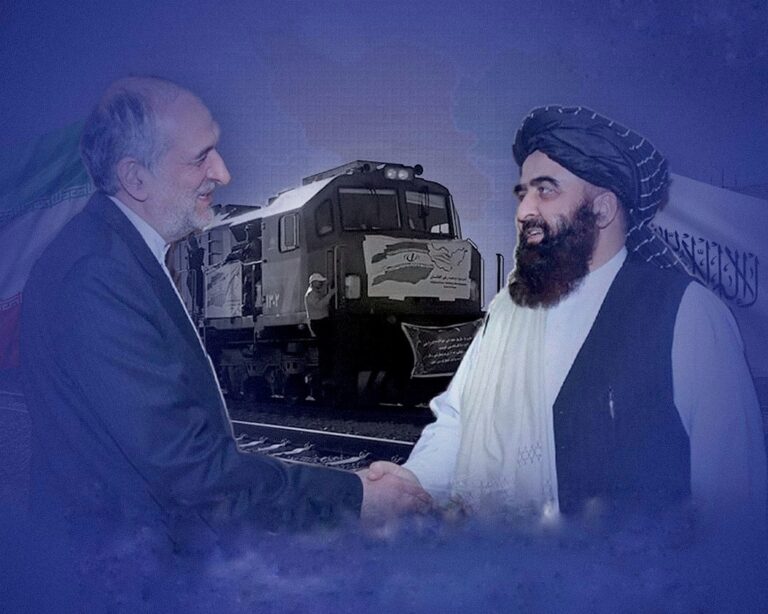সাম্প্রতিক সময়ে তিউনিসিয়ার কিছু রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি প্রচলিত চিন্তার গণ্ডি পেরিয়ে বেশ কিছু প্রবন্ধ ও বিবৃতি প্রকাশ করেছেন। এসব লেখায়, নিজেদের অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, তাঁরা বলছেন—তিউনিসিয়ার বর্তমান সংকট থেকে বের হতে হলে পুরোনো বিদ্বেষ ও তীব্র আদর্শিক বিভাজনের অধ্যায় বন্ধ করতে হবে। দরকার একটি নতুন যুগের সূচনা, যার ভিত্তি হবে পারস্পরিক স্বীকৃতি, বিশ্বাস আর সম্মান। শুদ্ধতার মুখোশ কিংবা প্রতিপক্ষকে শয়তান হিসেবে দেখার রাজনীতি থেকে সরে এসে দরকার খোলামেলা সংলাপ—যার মাধ্যমে গড়ে তোলা যাবে একটি যৌথ রাজনৈতিক চুক্তি, যা দেশের জন্য এক নতুন পথের ভিত্তি রচনা করতে পারে।
তবে এই আহ্বান ঘিরে দেখা দিয়েছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া। কেউ এটিকে সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত বলে স্বাগত জানিয়েছেন, আবার কেউ অতীতে এসব ব্যক্তির ভূমিকার দিকে ইঙ্গিত করে তাঁদের সদিচ্ছা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। আবার কারও মতে, এই উদ্যোগ সফল করার মতো পরিবেশ বা প্রস্তুতি এখনো পুরোপুরি তৈরি হয়নি।
প্রধান প্রশ্নটা এখন এই—এই নতুন চিন্তাগুলো কি তিউনিসিয়ার জনপরিসরে নতুন কোনো রাজনৈতিক গতি সঞ্চার করতে পারবে? এমন এক রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে তুলতে পারবে কি, যা দেশটির রাজনীতিকে নতুন সম্ভাবনা ও অভিমুখ দেবে?
উল্লেখ্য, সংলাপের ডাক তিউনিসিয়ার রাজনীতিতে নতুন কিছু নয়। বরং, যখনই জনপরিসরে স্থবিরতা ও হতাশা দেখা দিয়েছে, তখনই বিশ্লেষকেরা সংলাপের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। বিশেষ করে এমন প্রেক্ষাপটে, যেখানে বর্তমান ক্ষমতাসীন কর্তৃত্ববাদী শাসন একের পর এক রাজনৈতিক পরিসর সংকুচিত করে চলেছে। রাজনীতি প্রায় নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে, রাজনৈতিক দল ও নাগরিক সংগঠনগুলোকে ক্রমেই প্রান্তে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। এই বাস্তবতায় প্রশ্ন থেকেই যায়—সংলাপের এই নতুন আহ্বান কি বাস্তব কোনো পরিবর্তনের সূচনা করতে পারবে?
ভাঙনের রাজনীতি
গত পাঁচ দশকের বেশি সময় ধরে তিউনিসিয়ার রাজনীতি ছিল এক তীব্র মেরুকরণের শিকার। দেশের প্রধান রাজনৈতিক ধারাগুলোর মধ্যে যেমন বিভাজন ছিল, তেমনি প্রতিটি ধারার অভ্যন্তরেও ছিল বিভক্তি ও মতানৈক্য। একদল থেকে আরেক দলের জন্ম, দল ভাঙা-গড়ার এই চক্র অনেকটাই এই বিভাজনের ফল।
বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ছিল সেই জায়গা, যেখানে সমাজের গভীর মেরুকরণ সবচেয়ে প্রকটভাবে ফুটে উঠত। বামপন্থী, ইসলামপন্থী আর জাতীয়তাবাদী ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে সংঘাত কেবল আদর্শিক লড়াইয়ে সীমাবদ্ধ থাকেনি—রক্তাক্ত সংঘর্ষ, হানাহানি আর সহিংসতায় বারবার রঞ্জিত হয়েছে ক্যাম্পাসের মাটি।
আপাতদৃষ্টিতে সবাই ‘স্বাধীনতা’র নামে স্লোগান দিলেও, আসলে প্রতিটি পক্ষই চেয়েছিল তাদের বিরোধীদের সেই স্বাধীনতার আওতার বাইরে রাখতে। একদল যেমন অন্য দলের কণ্ঠরোধ করতে উঠেপড়ে লাগত, অন্যদলও পাল্টা জবাব দিত আরও রুদ্ররোষে। এভাবে স্বাধীনতার ডাক যেন পরিণত হয়েছিল এক ধরনের একচেটিয়া দাবিতে—‘স্বাধীনতা শুধু আমার জন্য, আমার মতের জন্য, আমার আদর্শের জন্য!’
এই চিত্রটি প্রেসিডেন্ট বোরগুইবা থেকে শুরু করে বেন আলীর শাসনামল পর্যন্ত মোটামুটি একই রকম ছিল। এই দীর্ঘস্থায়ী পরিস্থিতির মাঝে চারটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য, যা তিউনিসিয়ার রাজনৈতিক ধারাবাহিকতায় কিছুটা ভিন্নতা আনে।
প্রথম ঘটনা
১৯৮১ সালের ৬ জুলাই। আনুষ্ঠানিকভাবে রাজনীতিতে প্রবেশের সময় ইসলামপন্থী ‘ইত্তিজাহ ইসলামি’ (পরবর্তীতে ‘আন-নাহদা আন্দোলন’) যে দলিল প্রকাশ করে, তা ছিল একটি ব্যতিক্রমী রাজনৈতিক প্রস্তাবনা।
সেই দলিলে তারা বলেছিল, মতপ্রকাশ, সংগঠন ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা সহ সব ধরনের নাগরিক অধিকার রক্ষা, জাতীয় সব শক্তির সঙ্গে মেলামেশা, সর্বস্তরের রাজনৈতিক ও সামাজিক পক্ষগুলোর অংশগ্রহণে একটি সার্বিক জাতীয় সংলাপ, এবং ন্যায় ও স্বাধীনতার ভিত্তিতে নতুন তিউনিসিয়া গঠনের জন্য সম্মিলিত উদ্যোগ।
দ্বিতীয় ঘটনা
১৯৮৪ সালের নভেম্বর মাসে ইসলামপন্থী ছাত্ররা ‘একক ছাত্র সনদ’ নামে একটি প্রস্তাব তোলে। এর লক্ষ্য ছিল ছাত্রদের নিজস্ব মত অনুযায়ী প্রতিনিধি নির্ধারণের স্বাধীনতা দেওয়া।
এই সনদটি ছিল তাদের এই বিশ্বাসের প্রকাশ যে, উন্মুক্ত সংলাপই একটি গণতান্ত্রিক ও স্বাধীন সিদ্ধান্ত তৈরির একমাত্র উপায়।
তবে অন্যান্য ছাত্র সংগঠনগুলো এই উদ্যোগ প্রত্যাখ্যান করে। কেউ কেউ ইতিহাসের একপাক্ষিক ব্যাখ্যার ওপর ভিত্তি করে নতুন ছাত্র ইউনিয়ন গঠনের পথেও হাঁটে।
‘একক ছাত্র সনদ’ ধারণার উৎপত্তি হয়েছিল ১৯৭০-এর দশকের শেষ দিকে ইসলামপন্থী ছাত্রদের দেওয়া একটি স্লোগান থেকে, ‘আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং দেশে স্বাধীনতা চাই।’
তখন পুরো ছাত্র অঙ্গনে বামপন্থী মার্কসবাদীদের আধিপত্য ছিল এবং ইসলামপন্থী ধারাটি ছিল সরকারের দমন-পীড়নের শিকার।
তৃতীয় ঘটনা
২০০৫ সালের ১৮ অক্টোবর। ইসলামপন্থী, বামপন্থী, জাতীয়তাবাদী ও উদারপন্থী বিরোধী শক্তিগুলোর নেতারা যৌথভাবে একটি অনশন ধর্মঘট শুরু করেন। এই কর্মসূচির মূল দাবি ছিল রাজনৈতিক ও মানবাধিকারের প্রশ্নে কিছু মৌলিক পরিবর্তন আনা।
ডিসেম্বরেই এই আন্দোলন ‘১৮ অক্টোবর কমিটি ফর রাইটস অ্যান্ড ফ্রিডমস’-নামে একটি যৌথ প্ল্যাটফর্মে রূপ নেয়। যা হয়ে ওঠে ইসলামপন্থী ও ধর্মনিরপেক্ষদের মধ্যে সংলাপের প্রথম যৌথ মঞ্চ।
এই মঞ্চ থেকে প্রকাশিত ‘১৮ অক্টোবর ২০০৫ ঘোষণাপত্র’ ছিল ঐতিহাসিক এক দলিল। প্রথমবারের মতো ইসলামপন্থী ও ধর্মনিরপেক্ষরা একত্র হয়ে মৌলিক স্বাধীনতা ও মানবাধিকারের পক্ষে একটি ন্যূনতম ঐক্যমত্যে পৌঁছায়। তারা বলে, স্বাধীনতার কিছু মৌলিক বিষয় নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করা দরকার, এবং একটি পূর্ণাঙ্গ জাতীয় সংলাপ প্রয়োজন, যা একটি গণতান্ত্রিক অঙ্গীকার প্রতিষ্ঠা করবে এবং দেশের প্রতিটি নাগরিকের সমান অধিকার নিশ্চিত করবে।
‘১৮ অক্টোবর কমিটি ফর রাইটস অ্যান্ড ফ্রিডমস’ ছিল এমন একটি জায়গা, যেখানে নানা মত ও পথের মানুষ একসঙ্গে বসে কথা বলেছিল, মত বিনিময় করেছিল। এটি তিউনিসিয়ার রাজনীতিতে গণতন্ত্র, স্বাধীনতা ও অধিকার নিয়ে সচেতনতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রেখেছিল। সেই সময়ের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে এই মঞ্চ ছিল বিরোধীদের ঐক্য ও যৌথ লড়াইয়ের এক বড় পদক্ষেপ।
হারিয়ে যাওয়া এক সম্ভাবনা
যখন সময়টা ছিল ‘১৮ অক্টোবর কমিটি ফর রাইটস অ্যান্ড ফ্রিডমস’র অর্জনের ওপর ভিত্তি করে এগিয়ে যাওয়ার—বিশেষ করে, গণতান্ত্রিক রূপান্তরের সময়কাল পরিচালনার জন্য প্রস্তাবিত ‘গণতান্ত্রিক অঙ্গীকার’-এর ধারণাটিকে বাস্তবায়নের—তখনই বিপরীত এক চিত্র দেখা গেল। বিপ্লবের পরপরই মতাদর্শগত মেরুকরণ ফিরে এলো আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় আরও বেশি তীব্রতা নিয়ে। পুরো একটি দশকজুড়ে, ২০১১ থেকে ২০২১ পর্যন্ত, এই বিভাজন তিউনিসিয়ার গণতান্ত্রিক যাত্রায় দাগ রেখে যায়।
এই প্রেক্ষাপটে ‘বিপ্লব, রাজনৈতিক সংস্কার ও গণতান্ত্রিক রূপান্তরের লক্ষ্য বাস্তবায়নে উচ্চপর্যায়ের কমিটি’ গঠনের সিদ্ধান্ত ছিল যথাযথ। সংবিধান বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক আয়াদ বেন আশুরের নেতৃত্বে এই কমিটি তৈরি হয় একটি সমঝোতার প্ল্যাটফর্ম হিসেবে। যেখানে রাজনৈতিক দল, নাগরিক সমাজের সংগঠন, শ্রমিক সংগঠন, স্বাধীন ব্যক্তিত্ব, তরুণ এবং নারীদের প্রতিনিধিত্ব ছিল। উদ্দেশ্য ছিল—সব পক্ষকে নিয়ে রূপান্তরের পথ ও কাঠামো নির্ধারণ করা।
কিন্তু বাস্তবে এই কমিটির কার্যপরিবেশ ছিল তীব্র মতাদর্শিক উত্তেজনায় পরিপূর্ণ। একদিকে ছিল নিজেদের স্বভাবগতভাবেই আধুনিকতাবাদী দাবি করা একটি পক্ষ, অন্যদিকে ছিল পরিচয়ভিত্তিক রাজনীতির অনুসারীরা—যার মূলধারা ছিল ইসলামপন্থী ‘আন-নাহদা’ আন্দোলন।
কমিটির কাজকর্মও সেই উত্তেজনার ছাপ বহন করে। ভেতরের শক্তির ভারসাম্য অনুযায়ী যেসব সিদ্ধান্ত হয়েছে, তা আদতে ছিল একপাক্ষিক। পরে কমিটির সভাপতি স্বীকারও করেন, তাঁরা ইচ্ছাকৃতভাবে এমন নীতিমালা ও আইন তৈরি করেছিলেন, যাতে ‘আন-নাহদা’ তাদের নির্বাচনী জনপ্রিয়তা থাকা সত্ত্বেও ক্ষমতায় যেতে না পারে। অপরদিকে, তুলনামূলকভাবে জনসমর্থন কম থাকা ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলো যেন সরকারে অংশ নিতে পারে এবং প্রভাব বজায় রাখতে পারে—এমন নিশ্চয়তা রাখা হয়েছিল।
ফলে, যে ‘সমঝোতার রাজনীতি’ দিয়ে রূপান্তরপর্ব চালানোর কথা ছিল, তা বাস্তবে ভেস্তে যায়। বরং এই কমিটি এমন কিছু অন্তর্ঘাতমূলক ব্যবস্থার বীজ বপন করে যায়, যেগুলোর বিস্ফোরণ ঘটে নতুন শাসকদের পথেই। এতে করে পুরো রূপান্তরপ্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হয় এবং ২০২১ সালের জুলাইয়ে যে রাজনৈতিক পালাবদল বা অভ্যুত্থান ঘটে, সেটি এই প্রক্রিয়াকে একেবারে গুঁড়িয়ে দেওয়ার পথ তৈরি করে দেয়।
এই কমিটির প্রভাব শুধু তখনই সীমিত ছিল না—গত দশকের পুরো রাজনীতির গতিপথকেই নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করেছে। ঐক্যের বদলে তৈরি হয়েছে বিভাজন, সমঝোতার বদলে এসেছে বিদ্বেষ। সমাজে গভীর মেরুকরণ তৈরি হয়—একদিকে এমন এক শ্রেণি, যারা নিজেদের তিউনিসিয়ার অতীত ও ভবিষ্যতের প্রকৃত অভিভাবক মনে করে, মনে করে আধুনিক সমাজব্যবস্থার রক্ষাকর্তা তারাই। আর অন্যদিকে ছিল ইসলামপন্থী ‘আন-নাহদা’, যারা চেয়েছিল তাদের প্রতিনিধিত্বকারী নাগরিকদের জন্য পূর্ণাঙ্গ নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করতে—সমান মর্যাদা, অংশগ্রহণ ও স্বীকৃতির মাধ্যমে। এই চেষ্টার পেছনে তাদের লক্ষ্য ছিল রাজনৈতিক ভারসাম্য ফিরিয়ে আনা—যেখানে কেউ বাদ পড়ে না, কেউ প্রান্তিক থাকেনা।
এভাবেই, এক সম্ভাবনাময় পথ শেষ পর্যন্ত হারিয়ে গেল মেরুকরণ আর একপাক্ষিক দৃষ্টিভঙ্গির ধাক্কায়।
প্রতারিত এক বিপ্লব
যেভাবে ‘১৮ অক্টোবর কমিটি ফর রাইটস অ্যান্ড ফ্রিডমস’ ছিল একটি হাতছাড়া সুযোগ, সে একইভাবে বিপ্লবও হয়েছে প্রতারিত—ভিতরের থেকেও, বাইরের থেকেও। বিপ্লবের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে দেশের প্রভাবশালী বুদ্ধিজীবী মহলের বড় একটি অংশ, যারা জোর করে এমন এক পথ বেছে নিয়েছিলেন, যেটা ছিল সংলাপ, সহাবস্থান আর পারস্পরিক স্বীকৃতির সম্পূর্ণ বিপরীত। সেই পথ দেশকে ঠেলে দিয়েছিল পরিচয়ভিত্তিক বিচ্ছিন্নতা, তীব্র মতাদর্শিক মেরুকরণ আর সাংঘর্ষিক রাজনীতির আগুনে।
বিপ্লব-পরবর্তী সময়ে রাজনীতি যেমনটা হওয়ার কথা ছিল, বাস্তবে তা হয়নি। প্রত্যাশা ছিল—১৮ অক্টোবর কমিটি ফর রাইটস অ্যান্ড ফ্রিডমস যা শুরু করেছিল, তার ধারাবাহিকতায় একটি অংশগ্রহণমূলক গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া এগিয়ে যাবে। কিন্তু পরিবর্তে রাজনীতি মোড় নেয় ‘বেন আশুর কমিটি’র দিকেই। এখানে দেখা যায়, বেশিরভাগ ধর্মনিরপেক্ষপন্থী নেতৃত্ব সংলাপ ও মতবিরোধীদের সঙ্গে একত্রে চলার নীতি ত্যাগ করে, বিশেষ করে ইসলামপন্থী, আন নাহদা দলের সঙ্গে।
২০১১ সালের অক্টোবরের সাংবিধানিক পরিষদ নির্বাচনে আন নাহদা দল ৩৭.০৪ শতাংশ ভোট পেয়ে প্রথম স্থান অর্জন করে, পায় ৮৯টি আসন—দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা দলের চেয়ে ৬০টি বেশি।
তবে এই জয়ে আত্মতুষ্টিতে না ভুগে আন নাহদা সব রাজনৈতিক দলের প্রতি আহ্বান জানায়—একটি ‘ঐতিহাসিক জোট’ গঠনের জন্য, যেন সবাই মিলে সরকার ও পরিষদের কাজ ভাগ করে নিয়ে চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করতে পারে। কিন্তু সেই প্রস্তাবে সাড়া দেয়নি অধিকাংশ দল, এমনকি অনেকে আগে ‘১৮ অক্টোবর কমিটি ফর রাইটস অ্যান্ড ফ্রিডমস’-তে তাদের সঙ্গী ছিলেন। কেবল দুটি ধর্মনিরপেক্ষ দল—তাকাতুল এবং কংগ্রেস ফর দ্য রিপাবলিক—এই আহ্বানে সাড়া দেয়।
আন নাহদা আবারও তাদের ইসলামিক রাজনৈতিক পরিচয়ের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে—যার মূলনীতি পারস্পরিক ভিন্নমতকে স্বীকৃতি দেওয়া, গণতান্ত্রিক উপায়ে তা পরিচালনা করা, এবং একচেটিয়া রাজনীতি থেকে সরে এসে সবাইকে নিয়ে একটি পরিচ্ছন্ন রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে তোলা।
এখানেই আবার স্পষ্ট হয়ে ওঠে দুই বিপরীত ধারা। একদিকে ঐক্যের প্রস্তাব—যেখানে সবাই অংশ নিতে পারে, সম্মান পায়, আরেকদিকে বিভাজনের রাজনীতি—যেখানে নিজেকে আধুনিক, প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক দাবি করে অন্যদের বর্জন করা হয়।
ত্রয়ী জোটের রাজনৈতিক টানাপোড়েন ও সংকটের সূচনা
ত্রয়ী জোটের রাজনৈতিক যাত্রা মসৃণ ছিল না। দুটি রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড, ‘আত্মত্যাগ আন্দোলন’ এবং দেশব্যাপী অস্থিরতার মধ্য দিয়ে এর পথচলা শুরু হয়। তবে আন-নাহদা সংলাপের পথ বেছে নিয়ে জাতীয় ঐকমত্য গঠনে অগ্রণী ভূমিকা রাখে, যা সহিংসতা এড়িয়ে দেশকে স্থিতিশীলতা পর্যন্ত নিয়ে যায়।
এই সংলাপের ইতিবাচক ফলাফল ছিল সুস্পষ্ট—একটি দক্ষ টেকনোক্র্যাট সরকার গঠন, সর্বসম্মতিতে সংবিধান প্রণয়ন, স্বাধীন নির্বাচন কমিশন গঠন এবং সময়মতো নির্বাচন অনুষ্ঠানের রোডম্যাপ।
কিন্তু এই ঐকমত্যের ভিত্তি ছিল দুর্বল। ২০১৪ সালের নির্বাচনের পরই এর কার্যকারিতা হারায়, কারণ জোটের দলগুলো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মৌলিক নীতিগুলো নিয়ে সমঝোতায় পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়। ২০১৪ সালের সংবিধানে অনেক অগ্রগতিমূলক বিষয় থাকলেও সেগুলো বাস্তবায়িত হয়নি।
তবুও আন-নাহদা ঐক্যবদ্ধ রাজনীতির চেষ্টা চালিয়ে যায়। তারা ২০১৪ সালের নির্বাচনে বিজয়ী দল নিদা তুনুসের সঙ্গে জোট গঠন করে। কিন্তু এই জোট স্থায়ী হয়নি—২০১৮ সালে আন-নাহদা নিদা তুনুস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গঠিত নতুন দল ‘তাহিয়া তুনুস’-এর সঙ্গে হাত মেলায়, যার নেতৃত্বে ছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইউসুফ শাহেদ।
রাজনৈতিক মোড় ও নতুন সংকট
এই জোটবদলের পরিণতি ছিল গভীর ও দীর্ঘ সংকট। ২০১৯ সালের নির্বাচনে এর প্রভাব স্পষ্ট হয়—আন-নাহদা আশানুরূপ ফলাফল করতে ব্যর্থ হয়, আর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বিজয়ী হন স্বতন্ত্র প্রার্থী কায়েস সাইদ।
২০২১ সালের ২৫ জুলাইয়ের রাষ্ট্রপতির একতরফা ক্ষমতা দখলের পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে। দেশ পুনরায় একনায়কতন্ত্রের দিকে ফিরে যায়, যা বিপ্লবের আদর্শ, গণতান্ত্রিক রূপান্তর এবং আন-নাহদার সমন্বয়বাদী রাজনীতির সম্পূর্ণ বিপরীত। তাদের লক্ষ্য ছিল মতপার্থক্য সত্ত্বেও শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তর ও সর্বজনীন অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। কিন্তু বাস্তবে তা আর সম্ভব হয়নি।
অভ্যুত্থান: একটি বেহাত সম্ভাবনা
২০২১ সালের ২৫ জুলাই রাত। তিউনিসিয়ার রাজনীতিতে নাটকীয় এক বাঁক। ইসলামপন্থী দল আন-নাহদা একেবারে একা হয়ে পড়ে। পার্লামেন্টের সামনে দাঁড়িয়ে দলটির নেতা ও স্পিকার রাশেদ ঘানুশি উচ্চারণ করেন একটি ঐতিহাসিক বাক্য—’এটা বৈধ সরকারের বিরুদ্ধে সরাসরি অভ্যুত্থান। তিনি আহ্বান জানান রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার।
সেসময় জনমনে চলছিল প্রবল আলোড়ন। অনেকেই ভেবেছিলেন, এ যেন ‘সংশোধনী অভিযান’। এক ধরনের শুদ্ধি অভিযান, যেখানে ২০১১ সালের বিপ্লবের পথ আবার ঠিক করে নেওয়া যাবে, তবে এবার আন-নাহদা ও তার মিত্রদের বাদ দিয়েই।
কিন্তু সময় গড়াতেই বদলে যেতে থাকে দৃশ্যপট। অভ্যুত্থানের প্রকৃত রূপ স্পষ্ট হতে শুরু করে। সমালোচনা চলতে থাকে। রাজপথে নামে ‘মোয়াতেনুন দিদ্দাল ইনকিলাব’ নামের সংগঠন, তিউনিসের শহরগুলোয় সাধারণ মানুষের কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে অভ্যুত্থানবিরোধী স্লোগান। সেই মুহূর্তে আন্দোলন যেন হয়ে ওঠে দুইটি প্রশ্নের জবাব—
প্রথম প্রশ্ন, ‘কি করবো?’—উত্তর: অভ্যুত্থানের বিরোধিতা করবো, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সংগ্রাম চালিয়ে যাবো।
দ্বিতীয় প্রশ্ন, ‘কিভাবে করবো?’—উত্তর: মতভেদ সত্ত্বেও সব গণতন্ত্রপন্থি শক্তিকে এক ছাতার নিচে আনবো।
কিন্তু বাস্তবতা ছিল ভিন্ন। সেই ছাতা কেবল ছাতাই রয়ে গেল। বিরোধীরা নানা জোট গড়ার চেষ্টা করলেও সেখানে ঠাঁই পেল কেবল একমত গোষ্ঠীরা। ফলে চার বছর পর এসে বিরোধীদের চেহারা দাঁড়িয়েছে কয়েকটি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন দলের সমষ্টি হিসেবে—যারা সবাই শাসকগোষ্ঠীর দমন-পীড়নের শিকার, কিন্তু নিজেদের মধ্যে বিভক্ত পুরোনো মতাদর্শ, অতীতের ব্যর্থতা ও ভবিষ্যতের ভিন্ন স্বপ্নে।
এই সময়ে প্রয়োজন ছিল—একটি জাতীয় সংলাপ, যা নিয়ে আসবে গণতন্ত্রপন্থিদের ঐক্য, প্রতিষ্ঠা করবে এমন একটি রাজনৈতিক কাঠামো, যা হবে অংশগ্রহণমূলক, সহনশীল এবং সব মতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। অথচ দেখা গেল উল্টো চিত্র—চলতে থাকে পারস্পরিক বর্জন, ঘৃণা ছড়ানো, দোষারোপ আর একে অপরকে ‘শয়তান’ আখ্যা দেওয়া।
যারা সাহস করে আলাদা কিছু বলার চেষ্টা করেছে, তাদের কণ্ঠরোধ করা হয়েছে উপহাস, অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্যের মাধ্যমে।
এই বাস্তবতায় তিউনিসিয়ার সামনে এখন দুটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ জরুরি হয়ে উঠেছে:
প্রথমত, বিরোধী গণতন্ত্রপন্থী গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে কিছু মৌলিক দাবিতে ন্যূনতম ঐকমত্য গড়ে তোলা—যেমন, অভ্যুত্থানের বিরোধিতা, রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বিচারের অবসান, এবং কুখ্যাত ডিক্রি ৫৪ বাতিল।
এই ঐক্যের কিছুটা ভিত্তি এখন আছে বটে, তবে সেটি গড়ে উঠেছে ভয় থেকে—দমন-পীড়নের ভয়। কিন্তু ভয় এক অস্থায়ী অনুভব, যা দ্রুত বদলে যেতে পারে। তাই এই ভিত্তিকে শক্ত রাজনৈতিক পরিকাঠামো বলা যায় না।
দ্বিতীয়ত, এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, একটি ঐতিহাসিক চুক্তির দিকে অগ্রসর হওয়া—যেখানে সব পক্ষ থাকবে নাগরিকত্বের ভিত্তিতে সমান মর্যাদায়, এবং অঙ্গীকার থাকবে স্পষ্ট মূল্যবোধের: গণতন্ত্র, মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা, পারস্পরিক সম্মান, শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তর, ও নির্বাচনের রায় মেনে নেওয়া।
এই পথে এখনো অনেকটা পথ বাকি। আছে বাধা, ক্লান্তি, ভুল বোঝাবুঝি। তবে আন্তরিকতা থাকলে এই পথে গড়ে তোলা সম্ভব একটি নতুন বিপ্লব—যে বিপ্লব বদলে দেবে পুরোনো বিভক্ত রাজনীতিকে, আর নিয়ে আসবে এমন এক নতুন রাজনীতি, যা হবে গণতন্ত্র, মুক্তি ও আধুনিকতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
এটাই হতে পারে মুক্তির নৌকা—যা তিউনিসিয়াকে বের করে আনবে অভ্যুত্থানের অন্ধকার গলি থেকে, পৌঁছে দেবে নাগরিক অধিকার, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে।
এই লেখায় প্রকাশিত দৃষ্টিভঙ্গি লেখকের নিজস্ব। মধ্যপ্রাচ্যের সম্পাদকীয় নীতির সাথে মিল থাকা জরুরি নয়।
সূত্র: আল জাজিরা