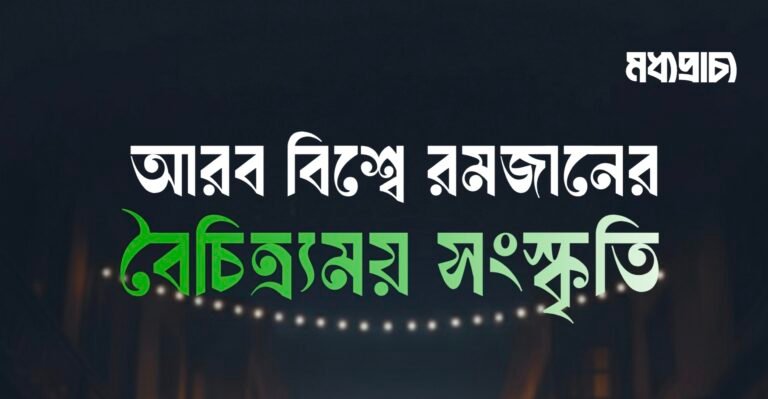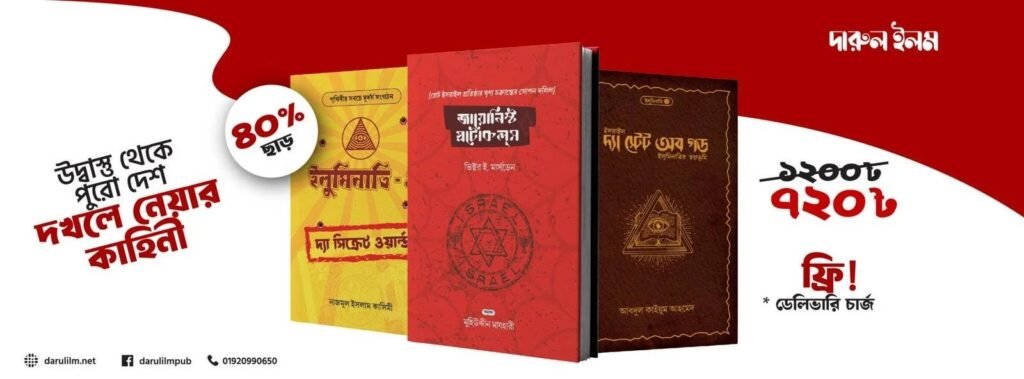গাজা আজ এক বেদনার শহর। চারদিকে শুধু কান্না আর বেদনার গল্প। তবু এই অসহায়তার মাঝেও কখনো কখনো জন্ম নেয় উজ্জ্বল কিছু মুহূর্ত, ছড়িয়ে পড়ে আশার আলো। তেমনই এক ব্যতিক্রমী গল্পের নায়ক তুরস্কের কুতাহিয়া ইউনিভার্সিটি অব হেলথ সায়েন্সের শিশু সার্জারি বিভাগের প্রধান, অধ্যাপক ডা. ইব্রাহিম ওউগুন।
স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে গাজায় গিয়েছিলেন তিনি। যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজায় শতাধিক অস্ত্রোপাচার করেছেন, চিকিৎসা দিয়েছেন সহস্রাধিক আহত মানুষকে। তাঁর এই নিঃস্বার্থ ত্যাগ শুধু আহতদের জীবনেই আলো ছড়ায়নি, বদলে দিয়েছে তাঁর নিজের জীবনকেও।
এই রক্তাক্ত মাটিতেই ডা. ওউগুনের পরিচয় হয় এক ফিলিস্তিনি নার্সের সঙ্গে, যিনি অপারেশন থিয়েটারে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করতেন। ধ্বংসস্তূপ আর অবিরাম বোমাবর্ষণের মধ্যেও তাঁদের মধ্যে গড়ে ওঠে এক অটুট বন্ধন। শেষ পর্যন্ত, জীবন-মৃত্যুর এই শহরেই তাঁরা একে অপরকে জীবনসঙ্গী হিসেবে বেছে নেন—যুদ্ধের ভেতর জন্ম নেয় ভালোবাসার এক অনন্য গল্প।
তবে গাজা ছাড়ার পথ সহজ ছিল না। স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে গাজা ত্যাগ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। শেষ পর্যন্ত তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রজব তাইয়্যেব এরদোয়ানের উদ্দেশে একটি ভিডিও বার্তা পাঠান তিনি। সেই বার্তার পরই নড়েচড়ে বসে তুরস্কের জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থা (এমআইটি)। তাদের উদ্যোগেই শেষ পর্যন্ত নিরাপদে গাজা থেকে সরিয়ে আনা সম্ভব হয় দুজনকে।

আনন্দ আর বেদনার গল্প
ইব্রাহিম ওউগুন—আমার তিন দশকেরও বেশি সময়ের সঙ্গী। বন্ধুত্বের বয়স ৩৫ বছর ছুঁইছুঁই। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, ব্যতিক্রমী দৃষ্টিভঙ্গি, গভীর বিশ্বাস আর অদম্য পরিশ্রমে সে তরুণ বয়স থেকেই আলাদা হয়ে উঠেছিল। আমি পড়েছি সাংবাদিকতা, সে চিকিৎসা শাস্ত্রে। পথ আলাদা হলেও যোগাযোগ কখনও বিচ্ছিন্ন হয়নি।
কিছুদিন আগে সে গিয়েছিল গাজায়। সেখান থেকে নিয়মিত ছবি আর ভিডিও পাঠাতো আমাকে, লিখে জানাতো গাজার ভয়াবহ পরিস্থিতি আর নিজের অভিজ্ঞতার কথা। টানা দুই মাস ধরে ইসরায়েলি হামলায় আহত শিশুদের অস্ত্রোপচার করেছে সে। নৃশংস বোমাবর্ষণের মধ্যেও দিনরাত পরিশ্রম করে সেলাই করেছে ওদের ক্ষত, সান্ত্বনা দিয়েছে বেদনায় কাতর শিশুদের।
একদিন সে একটি ভিডিও পাঠায় আমাকে—তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রজব তাইয়্যেব এরদোয়ানের উদ্দেশে। সে গাজা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য সাহায্য চায়। সদ্য বিবাহিত স্ত্রীর সঙ্গে সেখানে সে আটকে পড়েছে। ভিডিওটি সে আরও কয়েকটি জায়গায় পাঠায়। আমিও সেটি যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছে দিই। পরে জানতে পারি, তুরস্কের জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থা ওদের উদ্ধারে তৎপর হয়েছে।
শেষ পর্যন্ত অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে, ভয়ংকর এক যাত্রা শেষে তারা জর্ডান হয়ে তুরস্কে ফিরে আসে গত সপ্তাহে। দেশে ফেরার পরই আমি তাদের সঙ্গে দেখা করি। ইব্রাহিম আর তার স্ত্রী মিলে গাজার সেই দিনগুলোর অভিজ্ঞতা আমাকে শুনিয়েছেন। এযেন একসঙ্গে আনন্দ ও বেদনার এক দীর্ঘ অধ্যায়।
আপনি গাজায় কীভাবে গেলেন?
২০২৩ সালের ৭ অক্টোবরের ঘটনার পর থেকেই আমার মনে গেঁথে ছিল, গাজায় যেতে হবে, স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে। দীর্ঘদিন থেকেই আমি একজন শিশু সার্জন হিসেবে কাজ করছি। ভূমিকম্প, সন্ত্রাসী হামলা কিংবা বড় অনেক বিপর্যয়ের সময় স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করেছি। জানতাম, এমন অভিজ্ঞতা গাজায় শিশুদের চিকিৎসায় কাজে লাগবে। সেই বিশ্বাস থেকেই সিদ্ধান্ত নিই, যেভাবেই হোক, গাজায় যাব।
প্রথম দিকে গাজায় প্রবেশের একমাত্র পথ ছিল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তত্ত্বাবধানে তুরস্কের ফিলিস্তিনি চিকিৎসক সমিতি এবং ইউরোপের ফিলিস্তিনি চিকিৎসক সমিতির মাধ্যমে। তবে পুরো প্রক্রিয়াটা ছিল অত্যন্ত জটিল এবং ইসরায়েলের অনুমোদন ছাড়া কিছুই সম্ভব ছিল না। প্রায় এক বছর ধরে চেষ্টা চালিয়ে গেছি সেখানে পৌঁছানোর জন্য।
প্রথমবার ডাক পড়েছিল ২০২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে, জর্ডানের আম্মানে। আমরা ছিলাম চারজন তুর্কি চিকিৎসক। কিন্তু ইসরায়েল আমাদের মধ্যে তিনজনকে প্রবেশের অনুমতি দেয়নি। বাধ্য হয়েই ফিরে যেতে হয়েছিল তুরস্কে।
তবুও আমি হাল ছাড়িনি। আমার দৃঢ় সংকল্পের কারণে সংগঠনগুলো আবার আমার আবেদন বিবেচনা করে। শেষমেশ ২০২৫ সালের ২৮ জানুয়ারি, জর্ডান থেকে কারিম আবু সালেম সীমান্ত দিয়ে চিকিৎসকদের একটি দলের সঙ্গে গাজায় প্রবেশ করি।
গাজায় গিয়ে কী দেখলেন?
চারদিকে শুধু ধ্বংসস্তূপ। চোখে যা দেখেছ, ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। আমি এতটাই বিস্মিত হয়েছিলাম যে আশপাশে একটা গাছও চোখে পড়েনি, এমনকি কোনো জীবন্ত প্রাণীও না। রাস্তায় মুরগি, হাঁস, গরু, ছাগল—কোনো কিছুরই চিহ্ন নেই। অধিকাংশই মারা গেছে, আর যেটুকু টিকে ছিল, মানুষ বাঁচার তাগিদে খেয়ে ফেলেছে।
এই প্রথমবার কাছ থেকে দুর্ভিক্ষ দেখলাম। মানুষ কীভাবে বেঁচে থাকার জন্য ক্ষুধার সাথে যুদ্ধ করে, সেটা নিজের চোখে দেখেছি। এমন শোচনীয় অবস্থা আগে কখনো দেখিনি।
আপনি কি যুদ্ধবিরতির সময় গাজায় গিয়েছিলেন?
হ্যাঁ, তখন একটি যুদ্ধবিরতি চলছিল। দক্ষিণ গাজা থেকে উত্তর দিকে মানুষ ফিরে যাচ্ছিল দলে দলে। হাজারো মানুষ ফেরার পথ ধরেছিল। গাধার গাড়ি, হ্যান্ডকার্ট বা যেটা হাতে পেয়েছে, সেটাই বাহন। তাদের লক্ষ্য ছিল একটাই, নিজের ঘরটা একবার দেখা, সেটা ভেঙে গিয়েছে কি না, সেটাও গুরুত্বপূর্ণ নয়।
মানুষের এমন ঢল নেমেছিল যে গাড়িতে মাত্র ২০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে আমাদের লেগে গিয়েছিল প্রায় ৭ ঘণ্টা।
আমরা ছিলাম আরব আহলি হাসপাতালে, যেটি ব্যাপটিস্ট হাসপাতাল নামেও পরিচিত। তবে আমার মূল কাজ ছিল ‘অ্যামিটি অব পেশেন্টস’ হাসপাতালে, যেটি সেখান থেকে প্রায় ৩ কিলোমিটার দূরে। এটি ছিল এক ধরনের ট্রমা সেন্টার। সেখানে আহত শিশুদের নিয়েই আমাদের মূল কাজ চলতো।
শুধু চিকিৎসা নয়, প্রতিটি দিন ছিল একেকটা মানবিক ট্র্যাজেডির মুখোমুখি হওয়ার অভিজ্ঞতা।
হাসপাতালগুলোর অবস্থা কেমন ছিল? চিকিৎসাসেবা কতটা কার্যকর ছিল?
ইসরায়েল পরিকল্পিতভাবে গাজার হাসপাতালগুলোকে টার্গেট করেছে। সবচেয়ে বড় হাসপাতালগুলো গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। শত শত চিকিৎসক ও রোগী শহিদ হয়েছেন—তাঁদের অধিকাংশকেই হাসপাতালের চত্বরে কবর দেওয়া হয়েছে। যেসব হাসপাতাল কোনওভাবে কার্যকর ছিল, সেগুলোর উপরও বারবার হামলা চালানো হয়েছে। শুধুমাত্র কিছু অংশই সীমিতভাবে ব্যবহারের উপযোগী ছিল।
চিকিৎসকদের জন্য কম্পিউটেড টোমোগ্রাফি (সিটি স্ক্যান) যন্ত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই যন্ত্র দিয়েই শরীর বা মাথার ভেতরে বোমা কিংবা গুলির শার্ড শনাক্ত করে অস্ত্রোপচারের প্রস্তুতি নেওয়া যায়। অথচ ২৫ লাখ জনসংখ্যার গাজায় কার্যকর অবস্থায় থাকা সিটি স্ক্যান যন্ত্র ছিল মাত্র দুটি। আহতদের তড়িঘড়ি করে ওই দুটি হাসপাতালের একটিতে নেওয়া হতো। প্রয়োজনে সেখান থেকে আরেক হাসপাতালে নিয়ে অস্ত্রোপচার করতে হতো।
অন্য চিকিৎসা-সরঞ্জামের অবস্থা ছিল আরও করুণ। অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতি ছিল সীমিত, কাজ করতে হতো একেবারে দুর্বিষহ পরিবেশে। আমরা শিশুদের চিকিৎসা করতাম। তাদের ছোট শরীর বোমার টুকরা ও গুলির আঘাতে ঝাঁঝরা হয়ে যেত।
হাসপাতালগুলোতে বিদ্যুৎ ছিল না। জেনারেটরের সাহায্যে অপারেশন থিয়েটার চালু রাখা হতো। যুদ্ধবিরতির সময়ও গোলাবর্ষণ ও ড্রোন হামলা থামেনি। অনেক সময় আমাদের অস্ত্রোপচার করতে হতো বিস্ফোরণ আর ক্ষেপণাস্ত্রের শব্দের মধ্যেই।
একেকটি কক্ষে ৭–৮ জন রোগী পাশাপাশি রাখা হতো। কোথাও একটিও খালি বেড ছিল না। আর আমরা চিকিৎসকেরা থাকতাম একটুখানি ছোট ঘরে, যেখানে হিটারের ব্যবস্থাও ছিল না। প্রচণ্ড ঠান্ডায় ৫–৬ স্তরের কাপড় গায়ে দিয়ে ঘুমানোর চেষ্টা করতাম। এই তীব্র ঠান্ডা শিশুদের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব হতো না। অনেক নবজাতক শীতে জমে গিয়ে মারা যেত।
অচল শিশুটির কথা
একবার বোমা হামলার পর একটি শিশু আহত অবস্থায় হাসপাতালে আসে, বয়স আনুমানিক ৯ কিংবা ১০। সে তার বন্ধুদের সঙ্গে খেলছিল, এমন সময় একটি ড্রোন থেকে হামলা চালানো হয়। তার সব বন্ধুই মারা যায়। শিশুটির গলায় শার্ড ঢুকে মেরুদণ্ডে মারাত্মক আঘাত করে, ফলে সে পুরোপুরি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ে। গলায় একটি ছিদ্র করে তাকে লাইফ সাপোর্টে রাখা হয় যাতে সে শ্বাস নিতে পারে। সে শুধু কথা বলতে পারত, আর কিছুই না।
একদিন আমি তার পাশে বসেছিলাম। জিজ্ঞেস করলাম, ‘তুমি কেমন আছো?’ সে হেসে বলল, ‘আলহামদুলিল্লাহ।’ জীবনে কোনও মুহূর্ত আমাকে এতটা আলোড়িত করেনি। এমন ভয়ংকর অবস্থাতেও ছোট্ট ছেলেটি হাসছিল, আর আল্লাহর শোকর আদায় করছিল।
গাজার শিশুদের সাহস আমাকে সত্যিই অভিভূত করেছে। তারা রাস্তায়, পার্কে, মাঠে খেলত, এমনকি বোমা পড়ার সময়ও। আমি নিজে বোমার শব্দে আতঙ্কিত হয়ে পড়তাম, অথচ ওরা ছিল নির্ভীক। মৃত্যু, ক্ষেপণাস্ত্র, গোলাবর্ষণ—কোনও কিছুই যেন ওদের ছুঁতে পারত না।
গাজার মানুষের মানসিকতা কেমন ছিল?
গাজায় যে-ই যায়, সে শুধু সহায়তা দিতে যায় না—ফিরে আসে এক গভীর আত্মিক ও শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা নিয়ে। আমার নিজের অভিজ্ঞতাও তাই। আমি শুধু তাদের পাশে দাঁড়াইনি, বদলে গেছি নিজেও। গাজা আমাকে শিখিয়েছে, কীভাবে পুড়ে যাওয়া ভেতর থেকেও আলো ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে।
আমি দেখেছি, ফিলিস্তিনিরা জীবনের প্রতি কী অসম্ভব ভালোবাসা নিয়ে বাঁচে। তারা বাঁচতে চায়, হাসতে চায়, গড়তে চায়। কিন্তু মৃত্যুকেও তারা ভয় পায় না। বরং তাদের বিশ্বাস—শহীদরা কখনো মরে না, শাহাদাত জীবনেরই আরেক রূপ। তাই জীবনের মতো মৃত্যুকেও তারা আপন করে নেয়।
একবার আমি খুব ভীত হয়ে পড়েছিলাম, রকেটের শব্দে বুক কেঁপে উঠছিল। তখন আমার স্ত্রীর ভাই হেসে বলল, ‘যখন আমরা রকেটের শব্দ শুনি, তখন ভাবি—জান্নাত আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। তাহলে ভয় পাব কেন?’
আমি জীবনে এমন কোনো জাতি দেখিনি, যাদের আত্মিক শক্তি এত মজবুত, এত অটুট। তারা যখন নামাজে দাঁড়ায়, তখন তাদের মুখে উচ্চারিত আয়াতগুলো যেন তাদের বাস্তব জীবনেরই প্রতিচ্ছবি। বোমার শব্দের মধ্যেও তারা পড়ে—
وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ…
‘আমি অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করব কিছু ভয়, আর ক্ষুধা দিয়ে…’—সেই আয়াতগুলো। তখন মনে হয়, কোরআনের কথা যেন তাদের জীবনে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।
আমি দেখিনি কেউ কাঁদছে নিজের ঘর হারিয়ে, দেখিনি কোনো নারী সন্তান হারিয়ে হাহাকার করছে, না কোনো মানুষ অসহায়ের মতো ছটফট করছে। তারা ছিল জীবন্ত প্রতিচ্ছবি—
إنّا لله وإنّا إِلَيْهِ رَاجِعون
‘নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয়ই আমরা তাঁর কাছেই ফিরে যাব’—এই আয়াতের। তাদের সেই ধৈর্য আর আত্মসমর্পণ আমাদের হৃদয়ে এক অমোচনীয় ছাপ রেখে গেছে।
আরও অবাক হয়েছিলাম, যখন দেখলাম, যুদ্ধের মাঝেও নারীরা পরিচ্ছন্ন পোশাকে, হিজাব পরা, সন্তানের যত্নে ব্যস্ত। কোথাও অবহেলা, অগোছালো ভাব নেই। এমন পরিস্থিতিতেও তাদের আত্মমর্যাদা অটুট।
গাজায় জীবন আর মৃত্যু পাশাপাশি হাঁটে। চোখের সামনেই দেখা যায়, কে কখন চলে যায়, কে আবার থেকে যায়। অথচ এই মৃত্যুর ছায়ার মধ্যেই আমি অনুভব করেছি এমন এক আত্মিক প্রশান্তি, যা আমি এমনকি মক্কার নামাজেও পাইনি। গাজার আকাশ, বাতাস, কান্না, কুরআনের আওয়াজ সব কিছুতে ছিল এক গভীর ইমানি শক্তি।
সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় আমি দেখিনি কেউ ভিক্ষা করছে, দেখিনি চুরি, বিশৃঙ্খলা, কিংবা সেই নৈতিক ভাঙন যা সাধারণত যুদ্ধবিধ্বস্ত এলাকায় দেখা যায়। গাজার মানুষ যেন এক আলাদা জগতে বাঁচে। এক এমন জগতে, যেখানে মর্যাদা, ইমান আর দৃঢ়তা এখনো অটুট।
আপনি সেখানে এক গাজাবাসী নারীকে বিয়ে করেছেন। সেটা কীভাবে ঘটলো?
আমার খুব ইচ্ছে ছিল গাজার শহীদ সন্তানদের দায়িত্ব নেওয়ার, তাদের লালন-পালন করার—আজীবনের জন্য। কিন্তু পরে জানলাম, এটা আইনিভাবে সম্ভব নয়। বলা হলো, এ ধরনের কিছু করতে চাইলে, একমাত্র উপায় হলো এমন একজন বিধবাকে বিয়ে করা, যাঁর সন্তানাদি রয়েছে।
তখন আমি অবিবাহিত। ফেরার ঠিক দশ দিন আগে ইচ্ছা প্রকাশ করি, আমি এমন একজন বিধবাকে বিয়ে করতে চাই, যাঁর চার-পাঁচটি সন্তান রয়েছে। চিকিৎসকদের স্ত্রীরা মিলে এমন কাউকে খুঁজে দেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু কেউই রাজি হলেন না। কেউই গাজা ছাড়তে বা সন্তানদের অন্য দেশে নিয়ে যেতে রাজি না।
সেই সময় একজন নার্স ছিলেন। তার নাম ইমান। তিনি স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে আমাদের সঙ্গে অপারেশন থিয়েটারে কাজ করতেন। ছোটবেলায় মা-বাবা হারিয়ে এতিম হয়েছেন। নিজের জীবনটা উৎসর্গ করেছেন রোগীদের সেবা আর পরিবারের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়, ধীরে ধীরে হৃদ্যতা গড়ে ওঠে, জন্ম নেয় ভালোবাসা।
আমি বিষয়টি বলি হাসপাতালের পরিচালক ডা. ফাদেলকে। তিনি খুব আনন্দিত হন, পাশে দাঁড়ান, এমনকি ইমানের পরিবারের কাছে আমায় সঙ্গে করে নিয়ে যান। ইমান বিষয়টি তাঁর পরিবারকে জানান। তাঁরা বলেন, বাগদান নিয়ে আপত্তি নেই। তবে তখনকার পরিস্থিতিতে ইমানের পক্ষে গাজা ত্যাগ করা সম্ভব ছিল না, তাই বিয়ে হবে পরে—যখন যুদ্ধ শেষ হবে, পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে। আমি তাতে রাজি হয়ে যাই।
বাগদানের আয়োজন হলো গাজার রীতিতেই। হাসপাতালের এক কক্ষে পুরুষরা, আরেক কক্ষে নারীরা। সবার দোয়ায়, গান-আহ্বানে, ছোট্ট এক উৎসবের মতো করে বাগদান সম্পন্ন হলো।
এই সব কিছু হলো যুদ্ধের মধ্যেই?
আমরা সারাদিন আহতদের নিয়ে ব্যস্ত থাকতাম। অপারেশন শেষ করেই একটুখানি হাঁটতে যেতাম গাজার সমুদ্রতীরে। চারপাশে গোলার শব্দ, ক্ষেপণাস্ত্র, ড্রোন সব চলতেই থাকত। কিন্তু গাজার মানুষের মতো আমাদের মধ্যেও যেন অভ্যস্ততা এসে গিয়েছিল, শুরুর সেই ভয় আর ছিল না।
বাগদানের জন্য যা যা দরকার, খোলা থাকা অল্প কিছু দোকান থেকে তা সংগ্রহের চেষ্টা করি। গহনা জোগাড় হয় টুকরো টুকরো করে। আমার নিজের কোনো টাকা ছিল না, যা ছিল সব খরচ হয়ে গেছে। সহকর্মী চিকিৎসকদের কাছ থেকে ধার নিই। কিন্তু তখন এমন এক ভালোবাসা আর আন্তরিকতায় হৃদয় ভরে ছিল, অন্য কিছু লাগেনি।
শেষ পর্যন্ত, আমাদের বিয়ে সরকারি কাগজপত্রসহ সম্পন্ন হয় অর্ধেক ধ্বংস হয়ে যাওয়া একটি আদালত ভবনের এক অংশে।
আর এই সবকিছু, পরিচয়, সম্পর্ক, বাগদান, আর বিয়ে সব মিলিয়ে মাত্র সাত দিনের মধ্যে হয়ে যায়।
আপনি গাজায় দীর্ঘ সময় আটকে ছিলেন। এরপর কীভাবে সেখান থেকে বের হলেন?
যুদ্ধবিরতি শেষ হতেই আবার শুরু হয় বোমাবর্ষণ। তখন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আমাকে গাজা থেকে সরিয়ে নেওয়ার উদ্যোগ নেয়। কিন্তু আমি তখন গাজা ছাড়তে চাইনি, বরং কিছুদিন আরও থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। ঠিক সেই সময়েই ইমানের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। পরে আমরা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হই। তখন আমার ইচ্ছা ছিল, ইমানকে তার পরিবারের সম্মতিতে গাজা থেকে বের করে নিয়ে যাব। কিন্তু যুদ্ধের সময় গাজা ছাড়া ছিল প্রায় অসম্ভব। বিশেষ করে যখন ইমানের পাসপোর্টের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে এবং যেসব সরকারি ভবনে তা নবায়নের সুযোগ ছিল, সেগুলো তখন ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।
পরে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আমাকে আবার গাজা থেকে সরিয়ে নেওয়ার প্রস্তাব দিলে, আমি অনুরোধ করি যেন আমার স্ত্রীকেও সঙ্গে নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু তারা জানায়, এটা সম্ভব নয়। তখন আমি সিদ্ধান্ত নিই ইমানের সঙ্গেই গাজায় থেকে যাওয়ার। আমরা আরও কিছুদিন সেখানে কাটাই। এরপর, শেষ চেষ্টা হিসেবে ভাবলাম, আমাদের রাষ্ট্রপতি রজব তাইয়্যেব এরদোয়ানের সাহায্য চাই।
আপনি কীভাবে আপনার ভিডিওবার্তা রাষ্ট্রপতির কাছে পৌঁছালেন?
আমি ও আমার স্ত্রী একটি ভিডিও রেকর্ড করি, যেখানে জানাই—আমরা গাজায় বিয়ে করেছি, কিন্তু এখন এখান থেকে বের হতে পারছি না। তাই আমরা মাননীয় রাষ্ট্রপতির কাছে সাহায্যের আবেদন জানাই। যখনই ইন্টারনেট সংযোগ পাই, আমি ভিডিওটি তুরস্কে আমার কিছু পরিচিতজনের কাছে পাঠাই। আপনার কাছেও পাঠিয়েছিলাম।
এক-দু’দিনের মধ্যেই আমার ফোনে কল আসে। এক তুর্কি কর্মকর্তা জানান, তারা আমাদের গাজা থেকে সরিয়ে আনবেন এবং বলেন যেন আমরা কারিম আবু সালেম সীমান্তে পৌঁছানোর চেষ্টা করি। তখনই বুঝতে পারি, আমাদের ভিডিও বার্তাটি সত্যিই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের হাতে পৌঁছে গেছে।
আমরা তখনও ভাবছিলাম, ইমানকে গাজা থেকে বের করে আনা হয়তো অসম্ভব। তাই উত্তরের এলাকা থেকে দক্ষিণে যাওয়ার পরিকল্পনায় আমরা আশান্বিত হই। আমাদের সঙ্গে ছিল মাত্র একটি স্যুটকেস। ইমান জীবনে প্রথমবার গাজা ছাড়ছিল, তাই সে ব্যাগে কিছু শৈশবের স্মৃতি, কিছু ছবি নেয়, আর আমার হাত ধরে বেরিয়ে পড়ে।
দক্ষিণে পৌঁছানোর জন্য আমরা যা পেরেছি, তা-ই ব্যবহার করেছি। গাধার গাড়ি, ট্রাক্টরের ট্রেলার যা কিছু পাওয়া গেছে। কিন্তু এত কিছুর পরও আমরা সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছাতে পারিনি।
অবশেষে, আটদিন অপেক্ষার পর, আমাদের দুটি চিলিয়ান পরিবারের সঙ্গে একটি বহরে যুক্ত করা হয়। এইভাবেই আমরা সীমান্তে পৌঁছাতে সক্ষম হই। আমাদের ব্যাগ নিতে দেওয়া হয়নি। শুধু কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র নিয়ে, বাকি সব ফেলে রেখেই আমাদের সীমান্ত পার করানো হয়।
আমাদের নাম তালিকাভুক্ত থাকলেও, ইমানের পাসপোর্টের মেয়াদ শেষ থাকায় নতুন করে জটিলতা দেখা দেয়। ইসরায়েলি অংশে পৌঁছানোর পর, জর্ডানি কর্মকর্তারা আমাদের গ্রহণ করেন এবং জর্ডান সীমান্তে নিয়ে যান।
সেখানেও পাসপোর্ট জটিলতা তৈরি হয়। তবে তুর্কি দূতাবাসের কর্মকর্তাদের সহযোগিতায় আমরা সীমান্ত পার হই। আম্মানে পৌঁছানোর পর একদিনের মধ্যেই দূতাবাস ইমানের জন্য নতুন পাসপোর্ট ইস্যু করে। এরপর আমরা বিমানযোগে ইস্তানবুলে পৌঁছাই। ভিডিওটি পাঠানোর ১১ দিন পর আমরা তুরস্কে পৌঁছাতে সক্ষম হই।
এই অভিজ্ঞতা যেন এক সিনেমার কাহিনি—মরণঘাতী যুদ্ধ, দারিদ্র্য, ধ্বংসস্তূপ, দিনভর যাত্রা, উদ্বেগ আর প্রতীক্ষার গল্প। আমি বিশ্বাস করি, এই অভিজ্ঞতা সারাজীবন আমার মনে গেঁথে থাকবে। তবে আল্লাহ আমাদের জন্য একটি ঘরের ব্যবস্থা করেছেন, এবং গাজার শিশুদের মতো এক ঈমানদার প্রজন্ম গড়ে তোলার সুযোগ দিয়েছেন—এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। এজন্য আমরা আজীবন রাষ্ট্রপতি, জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান এবং যারা আমাদের সহায়তা করেছেন, তাদের সবার জন্য কৃতজ্ঞতা ও দোয়া জানিয়ে যাব।
ইমান, আপনি কেমন অনুভব করছেন?
বলতে গেলে, আমার ভেতরে এখন একসঙ্গে দুটো অনুভূতি। সুখ আর দুঃখ একসাথে দোলা দিচ্ছে। গাজা ছাড়ার ইচ্ছে আমার একদমই ছিল না। হাসপাতাল ছেড়ে যাওয়া, সহকর্মী ডাক্তারদের বিদায় বলা, আর রোগীদের ফেলে আসা—সবকিছুই ছিল খুবই কষ্টের। তবু ইব্রাহিমের সঙ্গে যে গভীর আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, সেটাই আমাকে শেষ পর্যন্ত চলে আসার সাহস দিয়েছে।
রাস্তায় অনেক কেঁদেছি, ভীষণ মন খারাপ ছিল। জীবনে কখনও গাজার বাইরে কোথাও যাইনি। যখন আমরা জর্ডানের সীমান্ত পার হচ্ছিলাম, তখন ইসরায়েলি সেনাদের দেখে ভেতরে ভেতরে ভয় আর অবাক লাগা, দুইই কাজ করছিল।
জর্ডান এরপর তুরস্কে এসে নতুন এক দুনিয়া দেখলাম। বুঝলাম, গাজার বাইরের পৃথিবী অনেক আলাদা। তবে গাজার প্রতি ভালোবাসা বা দায়িত্ববোধ একটুও কমেনি। আমরা এখন কুতাহিয়ায় থাকলেও গাজার জন্য কাজ করে যাচ্ছি, করে যাবো—একটা স্বাধীন ফিলিস্তিনের স্বপ্ন নিয়েই।
আমি বিশ্বাস করি, একদিন আমরা আবার ফিরে যাব—মুক্ত গাজায়, মুক্ত ফিলিস্তিনে। এই বিশ্বাস আমার হৃদয়ের গভীরে গেঁথে আছে।
প্রফেসর ড. ইব্রাহিম ওউইগুন ইতোমধ্যে কুতাহিয়ার হাসপাতালে তাঁর কাজে ফিরেছেন। তিনি তুর্কি সংস্কৃতি অনুযায়ী বিয়ের আয়োজন করছেন, যেখানে প্রেসিডেন্ট রজব তাইয়্যেব এরদোয়ান ও গোয়েন্দা প্রধান ইব্রাহিম কালিনকে আমন্ত্রণ জানানোর পরিকল্পনাও রয়েছে।
তাঁর মন এখনও গাজার সঙ্গেই জুড়ে আছে। তিনি নিয়মিত গাজার ত্রাণ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেন এবং সেখানকার চিকিৎসকদের পাশে দাঁড়ান, সহায়তা করে যান সবসময়।
সূত্র: আল জাজিরা