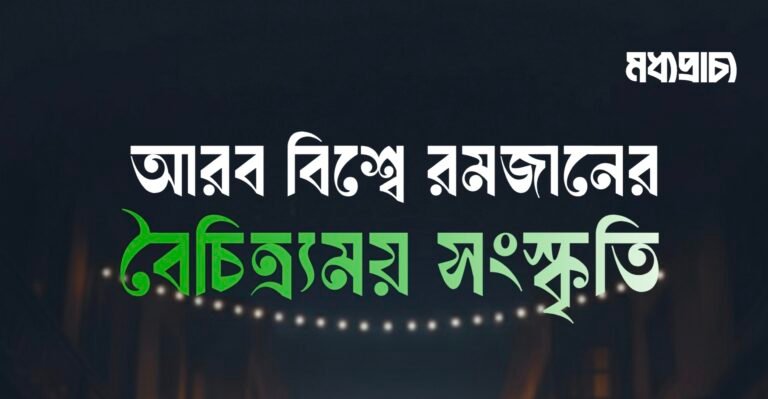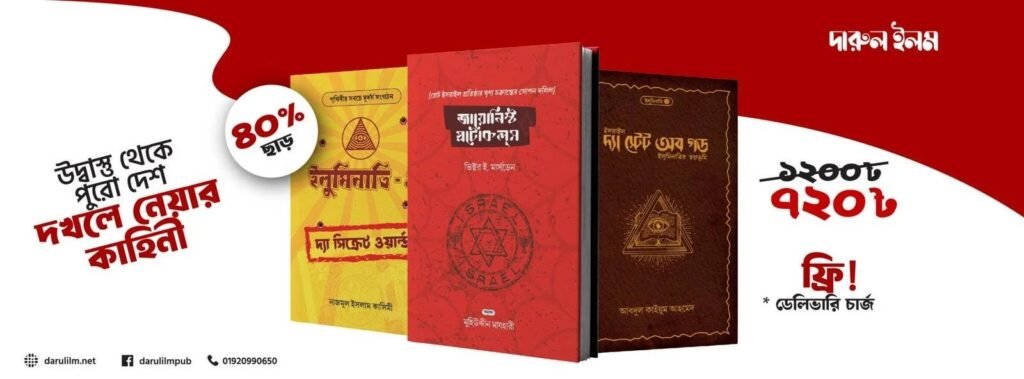২০২৩ সালের ৭ই অক্টোবর ‘তুফানুল আকসা’ অভিযান এ অঞ্চলের যুদ্ধকে ছড়িয়ে দিয়েছে আরো নানা ফ্রন্টে। ফলত, যুদ্ধের দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব ও প্রতিধ্বনিই সামগ্রিকভাবে এই অঞ্চলের ভবিষ্যৎ গঠনে ভূমিকা রাখছে।
ইসরায়েলি ফ্যাক্টর
যেকোনো ভূখন্ডের আঞ্চলিক ব্যবস্থা বিভিন্ন কারণে প্রভাবিত হয়। এর মধ্যে কিছু হয় বাহ্যিক (External Factors), যেমন আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার সাথে তাদের আচরনবিধি, প্রকৃতি; আর কিছু হয় অভ্যন্তরীণ (Internal Factors), যেমন সেই অঞ্চলের রাষ্ট্র ও শাসনব্যবস্থার কাঠামো। আরব আঞ্চলিক ব্যবস্থা—বা আরও ব্যাপকভাবে বললে মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা অঞ্চলও—এর ব্যতিক্রম নয়।
প্রথমত, এটি অনেক আগে থেকেই আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আসছে। বিশেষ করে স্নায়ুযুদ্ধের সময় এর কাঠামো, জোট এবং পক্ষগুলোর ওপর সরাসরি প্রভাব পড়েছিল। এরপর একমেরু বিশ্বব্যবস্থার উত্তরণ এই অঞ্চলের ওপর গভীর ছাপ ফেলেছে। একইভাবে এ অঞ্চলের কিছু বড় ও প্রভাবশালী রাষ্ট্রের কাঠামো ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনও একে প্রভাবিত করেছিল। উদাহারণত বলা যায়, মিশরে সামরিক অভ্যুত্থান, যা রাজতন্ত্রকে প্রজাতন্ত্রে রূপান্তর করেছিল এবং পরবর্তীতে অন্য দেশেও ছড়িয়ে পড়েছিল। এবং তারই ধারাবাহিকতায় ইরানের বিপ্লব ঘটে, যা শাহ শাসনের পতন ঘটায়।
তবে এই দুটি মৌলিক কারণ এবং অন্যান্য কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের পাশাপাশি, ‘ইসরায়েলি ফ্যাক্টর’ সব সময়ই এই অঞ্চলের গতিপথ নির্ধারণ ও পরিবর্তনের একটি প্রধান উপাদান হিসেবে কাজ করেছে।
আরব-ইসরায়েল যুদ্ধ থেকে শুরু করে মিশরের আনুষ্ঠানিক আরব ব্যবস্থা থেকে বিচ্যুত হয়ে ‘ক্যাম্প ডেভিড’ চুক্তি এমনকি উপসাগরীয় যুদ্ধগুলো পর্যন্ত, সবকিছুই ইসরায়েলের নিরাপত্তার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল, যদিও সেগুলোর পেছনে অন্যান্য পরিচিত কারণ বা অজুহাতও ছিল।
‘আরব বসন্ত’ নামে পরিচিত বিপ্লবগুলোর আগের সময়ে, এই অঞ্চলটি মূলত ইসরায়েলের সাথে সম্পর্কের পক্ষে বা বিপক্ষের অবস্থানের ভিত্তিতে বিন্যস্ত হত। অনেকে একে ‘আরব মডারেট’ (উদারপন্থী) এবং ‘প্রতিরোধ’ (রেজিস্ট্যান্স) ব্লকে ভাগ করতেন। বিপ্লবগুলোর সময়েও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে ইসরায়েলি প্রভাব স্পষ্ট ছিল।
বিপ্লব-পরবর্তী সময়ে ‘আব্রাহাম অ্যাকর্ডস’-এর আওতায় ইসরায়েলের সাথে স্বাভাবিকীকরণ ও সহযোগিতার চুক্তির লক্ষণীয় গতি দেখা যায়। আশা করা হচ্ছিল আরও কিছু আরব ও মুসলিম দেশ এতে যোগ দেবে, কিন্তু ‘তুফানুল আকসা’ সেই স্বপ্নে ছন্দপতন ঘটায় এবং প্রক্রিয়াটি সাময়িকভাবে পুরোপুরি কলাপস হয়ে যায়।
তুফানুল আকসা ব্লক
গত দুই বছরে গাজা উপত্যকা, পুরো ফিলিস্তিন এবং সামগ্রিকভাবে এই অঞ্চলে ৭ অক্টোবরের অভিযান, গণহত্যামূলক যুদ্ধ এবং যুদ্ধের আঞ্চলিক বিস্তারসহ যা কিছু ঘটেছে, তা এই অঞ্চলের ভবিষ্যৎ নিয়ে কিছু মৌলিক সত্য উন্মোচন করেছে।
প্রথম সত্য: ইসরায়েলের প্রকৃত রূপ এবং জায়নবাদী প্রকল্পের সারমর্ম। ইসরায়েল আরব ও ইসলামি বিশ্বের হৃদপিণ্ডে একটি পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী প্রকল্পের অগ্রবর্তী ঘাঁটি হিসেবে কাজ করছে। এবং স্পষ্ট যে, এই জায়নবাদি প্রকল্প মূলত অন্যকে নির্মূল করা, গণহত্যা, জাতিগত নিধন এবং মানবতাবিরোধী অপরাধের ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে। যুদ্ধ এই জায়নবাদিদের অনেক দুর্বলতা ও ত্রুটির উন্মেচন করে দিয়েছে, যা প্রমাণ করে যে সঠিক স্ট্রাটেজি থাকলে একে পরাজিত করা সম্ভব।
দ্বিতীয় সত্য: ইসরায়েলের যুদ্ধে পশ্চিমারা, বিশেষ করে আমেরিকা সরাসরি অংশীদার। পশ্চিমের সামরিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমর্থন ছাড়া এবং নিরাপত্তা পরিষদ ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সুরক্ষা ছাড়া ইসরায়েল জয়ী হওয়া তো দুরে থাক, এ যুদ্ধে টিকেই থাকতে পারত না। আমেরিকা গাজায় গোয়েন্দা তৎপরতা থেকে শুরু করে ইরানের পারমাণবিক স্থাপনায় হামলার মতো সরাসরি সামরিক হামলায় অংশগ্রহণও করেছে।
তৃতীয় সত্য: এই গণহত্যায় আরব রাষ্ট্রগুলোর আনুষ্ঠানিক অবস্থান ছিল অক্ষমতা, ব্যর্থতা এবং যোগসাজশের সংমিশ্রণ। দুই বছর ধরে গাজায় ত্রাণ পৌঁছে দিতে না পারা এই ব্যর্থতারই প্রমাণ।
এবং নিঃসন্দেহে, কাতারের দোহায় হামাসের মধ্যস্থতাকারী প্রতিনিধি দলের ওপর গুপ্তহত্যার প্রচেষ্টা এটা প্রমাণ করে যে, ‘তুফান’ পরবর্তী পর্যায়ে ইসরায়েল যেকোনো দেশের সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘন করতে প্রস্তুত। সে দেশের সাথে তাদের সম্পর্কের গভীরতা কতটুকু, বা তারা আমেরিকার কতটা ঘনিষ্ঠ, অথবা তারা যুদ্ধবিরতি ও বন্দি বিনিময়ের মধ্যস্থতাকারী কি না—তা ইসরায়েল তোয়াক্কা করে না।
যুদ্ধবিরতি যেহেতু আমেরিকার সিদ্ধান্তে এসেছে এবং ট্রাম্প যেভাবে নেতানিয়াহু সরকারকে নির্দিষ্ট কিছু সিদ্ধান্ত ও পথ অনুসরণে বাধ্য করছেন, তাতে আগামী দিনে ট্রাম্প প্রশাসনের অগ্রাধিকারগুলো বোঝা জরুরি। ট্রাম্প প্রশাসনের মূল লক্ষ্য এখন—যুদ্ধবিরতি স্থায়ী করা যাতে পূর্বের মতো গণহত্যার পুনরাবৃত্তি না ঘটে, এবং এর মাধ্যমে হারানো ভাবমূর্তি কিছুটা বিল্ডআপ করা, পাশাপাশি ‘শক্তির মাধ্যমে শান্তি’ (Peace through Strength) প্রতিষ্ঠা করা, অঞ্চলের কাঠামো পুনর্গঠন করা এবং ‘আব্রাহাম অ্যাকর্ডস’ বা স্বাভাবিকীকরণ প্রক্রিয়াকে পুনরায় এক্টিভেট করা। আর এই সবকিছুর পেছনে গণহত্যার অপরাধকে আড়াল করে ইসরায়েলকে এই অঞ্চলের সাথে আরও গভীরভাবে ও দৃঢ়ভাবে একীভূত করা।
আমেরিকার পরিকল্পনা
উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, এই অঞ্চলট বেশ কিছু পথ ও পরিস্থিতির (সিনারিও) মুখোমুখি হতে যাচ্ছে। এগুলো যে একে অপরের পরিপন্থী তা নয়; বরং একাধিক বা সবগুলোই বিভিন্ন পর্যায়ে বাস্তবায়িত হতে পারে।
প্রথমত: ট্রাম্পের মনোবাসনা হলো, পুরো অঞ্চলকে ইসরায়েলি ও আমেরিকান প্রভাবের অধীনে নিয়ে আসা। সামরিক শক্তি যেখানে ব্যর্থ হয়েছে, সেখানে রাজনীতি, কূটনীতি ও চাপের মাধ্যমে ইসরায়েলি স্বার্থ হাসিল করা। এর মধ্যে গাজা থেকে ফিলিস্তিনিদের উচ্ছেদের পরিকল্পনাও রয়েছে, যা মিশর ও জর্ডানের মতো দেশগুলোর জাতীয় নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতাকে হুমকির মুখে ফেলবে। এখানে ইসরায়েল হবে ওয়াশিংটনের সেই ‘লাঠি’ বা অস্ত্র, যা দেখিয়ে তারা এ অঞ্চলে আমেরিকান একক আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করবে।
দ্বিতীয়ত: গাজা, লেবানন, ইরান এবং সম্ভবত ইয়েমেন ও সিরিয়ায় নতুন করে যুদ্ধ শুরু করতে চাইবে ট্রাম্প ও নেতানিয়াহু প্রশাসন; হয় সামরিক আগ্রাসনের মাধ্যমে কিংবা হাই প্রোফাইল ব্যক্তিদের এসেসিনেশনের মাধ্যমে। ইসরায়েলের আগ্রাসনমূলক আকাঙ্ক্ষার বিস্তৃতি, গাজায় ‘প্রতিরোধ যোদ্ধাদের নিরস্ত্রীকরণ’, লেবাননে ‘হিজবুল্লাহকে নির্মূল’ এবং ইরানে ‘শাসনব্যবস্থার পতন বা পারমাণবিক প্রকল্প ধ্বংস’ করার মাধ্যমে তাদের ‘অসমাপ্ত কাজ’ শেষ করার ইচ্ছা এর বড় ইঙ্গিত। ইসরায়েল মনে করে, তারা ইতিমধ্যে বিশ্বজুড়ে সর্বোচ্চ নিন্দা ও চাপের মুখে পড়েছে, যার চেয়ে বেশি ঘৃনা আর চাপ হতে পারে না, তাই একই পথে চলতে তাদের আর কোনো দ্বিধা নেই।
অন্যান্য লক্ষণগুলোর দিকে তাকালে দেখা যায়, ২০২৬ সালের জন্য ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর বাজেট ধরা হয়েছে ৩৪.৫ বিলিয়ন ডলার—যা ২০২৩ সালের তুলনায় ৪২% এবং ২০২৫ সাল (তথা যুদ্ধ বিরতির বছর) এর তুলনায় ৫% বেশি। এর অর্থ এটি এক বিরাট যুদ্ধের বাজেট। এছাড়া ২০২৬ সাল হবে ইসরায়েলের জন্য একটি বিশেষ ও চূড়ান্ত নির্বাচনের বছর, যেখানে ফিলিস্তিনি ও আরবদের রক্ত ঝরিয়ে জনমত পাওয়ার প্রতিযোগিতা হতে পারে। পরিশেষে, ফিলিস্তিনিদের অধিকার ও আঞ্চলিক বাস্তবতা উপেক্ষা করে ‘শক্তির মাধ্যমে শান্তি’ চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা এই অঞ্চলকে একটি বারুদের স্তূপ বানিয়ে রাখবে, যা যেকোনো সময় জ্বলে উঠতে পারে।
তৃতীয়ত: এই যুদ্ধের একটি মধ্য বা দীর্ঘমেয়াদী সম্ভাবনা হলো—আশপাশের বিভিন্ন দেশে পুনরায় গণবিক্ষোভ ও বিপ্লব (আরব বসন্তের মতো) ফিরে আসতে পারে। ২০০৮-২০০৯ সালের ‘অপারেশন কাস্ট লিড’ যেমন ২০১১ সালে আরব বসন্ত উৎপাদনের কাঁচামাল তৈয়ার করেছিল, বর্তমান পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ, আরো ছোয়াচে। গাজার হামাস মুজাহিদদের বীরত্ব ও সেখানে বেসামরিক নাগরিকদের উপর চালানো ইসরায়েলি গণহত্যা পুরো দুনিয়ার সামনে, আর এর বিপরীতে আরব ও মুসলিম শাসকদের ব্যর্থতা জনগণের ক্ষোভকে আরও উসকে দিচ্ছে।
চতুর্থত: আমেরিকার প্রেসিডেন্ট যে স্বাভাবিকীকরণ বা ‘আব্রাহাম অ্যাকর্ডস’-এর কথা বলছেন, তা কেবল মিত্র দেশগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। তিনি ইরানকেও এই চুক্তিতে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছেন—সেই ইরান, যাকে কয়েক মাস আগেও ইসরায়েল ও আমেরিকা আক্রমণ করে সরকার ফেলে দেয়ার চেষ্টা করেছিল।
পঞ্চমত: নতুন বাস্তবতায় আঞ্চলিক সম্পর্কের ভিত্তি ও জোটগুলো পুনর্মূল্যায়ন করছে সবাই। বিশেষ করে কাতারের রাজধানী দোহায় ইসরায়েলি হামলার পর এটি আরও জরুরি হয়ে পড়েছে। আমরা ইতিমধ্যে তুরস্ক-মিশর সমন্বয় এবং সৌদি-পাকিস্তান সমঝোতার মতো নতুন নতুন অংশীদারত্বের আভাস দেখতে পাচ্ছি।
সারকথা হলো, এটি নিশ্চিত যে এই অঞ্চল নয়া দুনিয়ার এক নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করেছে, যেখানে আমেরিকা ও ইসরায়েল এই অঞ্চলে তাদের নিজস্ব এজেন্ডা চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে জোরালোভাবে। আরব লীগ এবং ওআইসির একটি যৌথ শীর্ষ সম্মেলনে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এরদোগান বলেছিলেন—‘গাজা হলো মুসলিম বিশ্ব রক্ষার দেয়াল’। এটি এখন কেবল স্লোগান নয়, বরং বাস্তবতায় পরিণত হয়েছে।
ইসরায়েল ও আমেরিকা গাজায় এক্টিভেট করা নৃশংস মডেলটিকেই লেবানন, সিরিয়া, ইরান ও ইয়েমেনসহ পুরো অঞ্চলে ছড়িয়ে দিতে চায়। তাই গাজায় তাদের এজেন্ডা রুখে দেওয়া কেবল ফিলিস্তিনিদের সমর্থনই নয়, বরং এই অঞ্চলের প্রতিটি দেশের নিজস্ব ও সামষ্টিক স্বার্থ রক্ষার জন্যই অপরিহার্য। রাজনৈতিক, নিরাপত্তা বা সামরিক কোনো পথই পূর্বনির্ধারিত বা অমোঘ নয়। এই অঞ্চলের দেশগুলো নিজেই এখানে প্রধান শক্তি হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারে এবং উপরে উল্লিখিত পরিস্থিতিগুলোর মধ্যে কোনটি বাস্তবে রূপ নেবে, তা নির্ধারণে তাদের সিদ্ধান্তই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হবে।
আল জাজিরার প্রতিবেদন থেকে ঈষৎ সংযোজিত