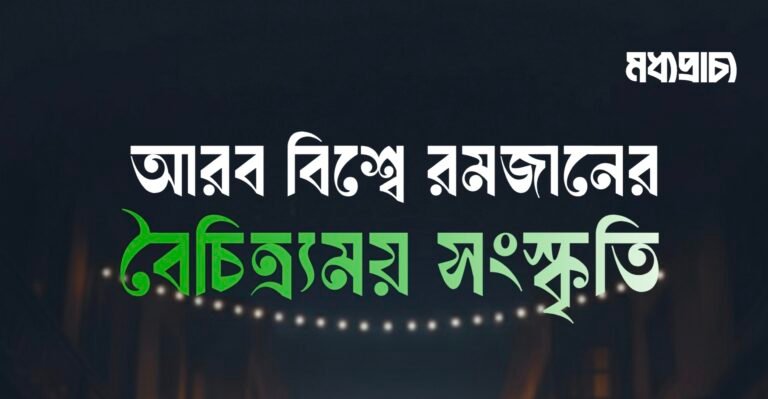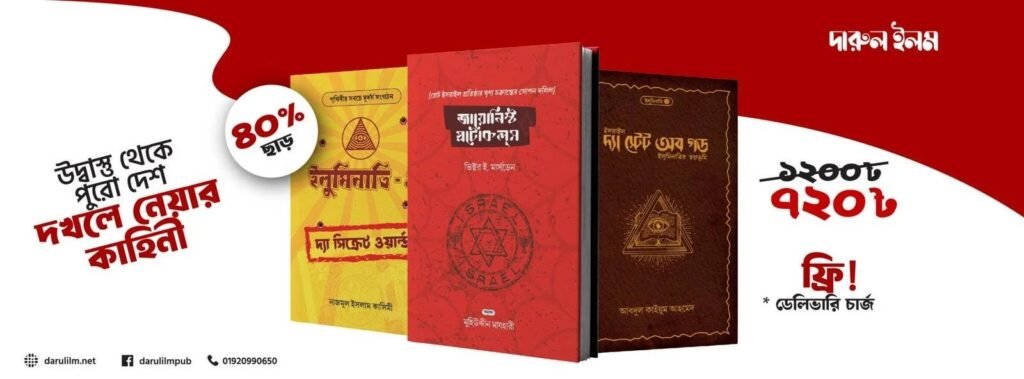গাজায় যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ চলছে,সেটা কোনো দুর্ঘটনা নয়। এটি একটি পরিকল্পিত এবং সংগঠিত যুদ্ধাপরাধের অংশ, যার মূল উদ্দেশ্য গাজাবাসীদের দমন করা এবং শেষমেশ তাদের নিজ ভূমি থেকে বিতাড়িত করা। এটি আসলে গণহত্যারই ভিন্ন আরেকটিরূপ, যা শুধু বোমা বা গুলিতে সীমাবদ্ধ নেই, যেখানে ক্ষুধাকে গণহত্যার অস্ত্র বানিয়ে ব্যবহার করা হচ্ছে।
ইসরায়েলের রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃত্বের একাধিক বৈঠকে যখন এই যুদ্ধকে কীভাবে ‘নিষ্পত্তিমূলক’ পর্যায়ে নেওয়া যায় তা নিয়ে আলোচনা চলছিল, তখন সম্পূর্ণ দখল কিংবা তথাকথিত ‘মানবিক করিডোর’ তৈরির মতো নানা প্রস্তাব উঠে আসে। এই প্রেক্ষাপটেই প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু আরও কঠোর অবরোধের প্রস্তাব দেন। তাঁর বিশ্বাস, এই কঠোর অবরোধই হামাসকে নতিস্বীকারে বাধ্য করবে।
কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, গাজা তো আগেই অবরুদ্ধ ছিল। তাহলে অবরোধ আরও কঠোর করার মানে কী? এর অর্থ হলো—যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর যে সামান্য পরিমাণ খাদ্যসামগ্রী খুবই সীমিতভাবে গাজায় ঢুকছিল, সেটাও পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া।
এই বাস্তবতা থেকে বোঝা যায় যুদ্ধের শুরু থেকেই গাজায় দুর্ভিক্ষকে একটি পরিকল্পিত অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। আর এখন সেটি আরও ভয়ংকর রূপ নিয়েছে। পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছেছে, যেখানে গাজাবাসীরা আগের মতো পশুখাদ্য কে উপযুক্ত করে রুটি বানানোর মতো উপায়ও খুঁজে পাচ্ছেন না।
এই খাদ্যাভাব, গণহত্যা,বাস্তুচ্যুতি আর লাগাতার বোমাবর্ষণ— সব মিলে এখন গণহত্যা তার ‘চূড়ান্ত পর্বে’ প্রবেশ করেছে।
একই সময়ে, ইসরায়েলি বাহিনী গাজার মধ্যাঞ্চলে আরও তীব্রভাবে ঢুকে পড়ছে। নতুন করে একটি ‘নিরাপত্তা করিডোর’ তৈরি করা হচ্ছে, যা দেইর আল বালাহকে আল-মাওয়াসি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিবে। এই করিডোরের পেছনে উদ্দেশ্য হলো, একটি দীর্ঘমেয়াদি বাস্তুচ্যুতি পরিকল্পনা।
ইসরায়েলি আলোচকরা যেসব ‘মানচিত্র’ নিয়ে দর কষাকষি করছে, সেখানে সব সময় এমন ব্যবস্থার সুযোগ রেখে দেওয়া হচ্ছে, যাতে ‘মানবিক করিডোর’ স্থাপন করা যায়। অথচ এই করিডোরগুলো আসলে আধুনিক যুগের বন্দিশিবির, যেখানে মানুষকে বন্দি করে রাখা হবে। রাজনৈতিক পরিচয়ের ভিত্তিতে তাদেরকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হবে।
এর মাধ্যমে প্রতিরোধ আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কিত কিংবা সমর্থনকারী পরিবারগুলোকে আলাদা করে টার্গেট করা হচ্ছে—এমনকি যদি তাদের কেউ সরাসরি যুদ্ধে যুক্ত নাও থাকে।
এইভাবেই, গাজায় চলছে এক নিষ্ঠুর, সুপরিকল্পিত ও বহুমাত্রিক গণহত্যা। আর এর অন্যতম প্রধান অস্ত্র এখন ক্ষুধা।
এদিকে তথাকথিত ‘গাজা হিউম্যানিটারিয়ান ফাউন্ডেশন’-এর আওতায় পরিচালিত সহায়তা বিতরণ কেন্দ্রগুলো বাস্তবে গাজাবাসীদের ওপর চাপ সৃষ্টি এবং তাদের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করার একটি যন্ত্রে পরিণত হয়েছে। এখানে যারা সাহায্যের আশায় আসছেন, তাদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে, খাবার দেওয়া হচ্ছে রক্তে চুবিয়ে । এর পেছনের উদ্দেশ্য হলো আতঙ্ক আর ভয়ের পরিবেশ তৈরি করে মানুষকে গাজা ছাড়তে বাধ্য করা, প্রতিরোধ আন্দোলনের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলা এবং সামগ্রিকভাবে সমাজের ভেতরে অস্থিরতা সৃষ্টি করা।
এই তথাকথিত ‘মানবিক’ প্রতিষ্ঠানের আরেকটি লক্ষ্য হচ্ছে যুদ্ধ ও অবরোধকে বৈধতা দেওয়া, যেন বলা যায় সহায়তা তো পৌঁছাচ্ছে। কিন্তু বাস্তবে এটি ইসরায়েলের আগ্রাসনকে আড়াল করার একটি পর্দা মাত্র। এর পাশাপাশি স্থানীয় কিছু মিলিশিয়াকে অস্ত্র সহায়তা দেওয়া হচ্ছে, যারা ইসরায়েলি স্বার্থে কাজ করছে। এসব বাহিনীকে ইসরায়েলি সেনারা নিরাপদ আশ্রয় দিচ্ছে। মূল উদ্দেশ্য গাজার সমাজকে ভেঙে দেয়া, প্রতিরোধ আন্দোলনকে দুর্বল করা, এবং ইসরায়েলের উপনিবেশবাদী নীতিকে বাস্তবায়নের জন্য একাধিক পথ খোলা রাখা।
এই দুর্ভিক্ষ নীতিকে কার্যকর ও দীর্ঘস্থায়ী রাখার জন্য যে বাস্তব পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তার কেন্দ্রেই রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রকাশ্য সম্পৃক্ততা। ২০২৫ সালের মে মাসে যুক্তরাষ্ট্র ঘোষণা দেয়—গাজায় সহায়তা পাঠাতে তারা নতুন একটি ব্যবস্থা চালু করছে, যেখানে বেসরকারি কোম্পানিগুলোর মাধ্যমে ত্রাণ সরবরাহ করা হবে। এই উদ্যোগের ভিত্তিতেই গঠিত হয় তথাকথিত ‘গাজা হিউম্যানিটারিয়ান ফাউন্ডেশন’। এই প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্বে আছেন জনি মুর—একজন মার্কিন ইভানজেলিক খ্রিস্টান পাদ্রি, যিনি ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রথম প্রেসিডেন্সির সময় হোয়াইট হাউজে উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেছিলেন।
এইভাবে, যুক্তরাষ্ট্র গাজায় দুর্ভিক্ষ সৃষ্টির ঘৃণ্য কাজে শুধু সহায়তা করছে না, বরং সরাসরি নেতৃত্ব দিচ্ছে। ফলে এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, নেতানিয়াহুর ও ওয়াশিংটনের মধ্যে ‘গণহত্যা’ ও ‘অবরোধ’ নিয়ে কোনও বাস্তব দ্বিমত নেই।
ইউরোপের ভূমিকাও আলাদা কিছু নয়। তারা একদিকে যেমন ইসরায়েলকে শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারে চরম ধীরগতি ও অনিচ্ছা দেখাচ্ছে, অন্যদিকে আবার এমন প্রচার চালাচ্ছে যা বাস্তবে এই দুর্ভিক্ষের সময়কাল বৃদ্ধি করছে।
১০ জুলাই ইউরোপীয় ইউনিয়নের পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ক প্রধান কাইয়া ক্যালাস ঘোষণা করেন, ইসরায়েলের সঙ্গে একটি সমঝোতায় পৌঁছানো হয়েছে । এতে গাজার মানবিক পরিস্থিতির উন্নয়ন ঘটবে, ত্রাণবাহী ট্রাকের সংখ্যা বাড়বে, সীমান্ত খুলে দেওয়া হবে এবং সহায়তার পথ পুনরায় চালু করা হবে।
কিন্তু বাস্তবে ঘটেছে তার বিপরীত। সহায়তা কমেছে, সীমান্ত বন্ধই থেকেছে, আর দুর্ভিক্ষ আরও ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। যার পরিণতিতে গাজায় দেখা দিয়েছে এক নজিরবিহীন মানবিক বিপর্যয়—একটি বাস্তব মৃত্যু উপত্যকা।
এদিকে, পশ্চিমা দেশগুলোর বিবৃতিগুলোর ইসরায়েলি নীতির ওপর বাস্তবে কোনো প্রভাবই পড়েনি। এমনকি ২১ জুলাই যে যৌথ বিবৃতিটি প্রকাশিত হয়, তাতেও সেই বাস্তবতার কোনো ব্যতিক্রম ছিল না। ঐ বিবৃতিতে ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, ইতালি, জাপান, কানাডা ও বেশ কিছু ইউরোপীয় দেশ গাজায় যুদ্ধ বন্ধের আহ্বান জানায়। বিবৃতিতে বলা হয়, ইসরায়েলি সরকারের সহায়তা বিতরণের পদ্ধতি ঝুঁকিপূর্ণ। এটি অস্থিতিশীলতা বাড়ায় এবং গাজার মানুষকে মানবিক মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করে। আরও বলা হয়, নাগরিক জনগণের জন্য মৌলিক মানবিক সহায়তা দিতে সরকারের অস্বীকৃতি গ্রহণযোগ্য নয়।
যুদ্ধের শুরু থেকে এ পর্যন্ত ইউরোপের বিভিন্ন দেশের বিবৃতি মূলত একই ধরনের ছিল। বাস্তবতায় তার ফলাফল শূন্য। ১০ জুন ব্রিটেন, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ও নরওয়ে একটি যৌথ বিবৃতিতে ইসরায়েলের জাতীয় নিরাপত্তামন্ত্রী ইতামার বেন গাভির এবং অর্থমন্ত্রী বেজালেল স্মোত্রিচের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। গাজা পরিস্থিতি নিয়ে তাদের ‘চরমপন্থী ও অমানবিক’ মন্তব্যের কারণেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তবে এসব সিদ্ধান্তের বাস্তব প্রভাব সীমিত। এসব বিবৃতি কার্যত নৈতিক অবস্থান জানানোর জন্যই দেওয়া হয়, যা মূলত রাজনৈতিক ও প্রচারণামূলক, এবং এর ফলে নেতানিয়াহুর নেতৃত্বাধীন সরকারের নিপীড়ন নীতিই আরো দীর্ঘস্থায়ী হয়। এই নীতি বাস্তবায়ন করে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী, যার কেন্দ্রে রয়েছে পরিকল্পিত দুর্ভিক্ষ। ফলে এসব আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া অনেকটা প্রতীকী প্রতিবাদেই সীমাবদ্ধ থেকে যায়।
এই প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে গণহত্যার অভিযোগে দায়ের করা মামলার কথাও উল্লেখযোগ্য। আদালতের বিভিন্ন নির্দেশনা সত্ত্বেও, ইসরায়েলের দমন-পীড়নের ধরনে কোনো পরিবর্তন আসেনি। বরং এই বর্বরতা নির্বিচারে চলতে থাকায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার—বিশেষ করে বিচার ও আইনি কাঠামোর—সীমাবদ্ধতা। এই ব্যর্থতার ভয়াবহ মাশুল আজ গাজার মানুষ দিচ্ছে, যেমনটা অতীতেও পুরো ফিলিস্তিনি জাতিকে দিতে হয়েছে।
গণহত্যার হাতিয়ার হিসেবে প্রকাশ্য ও সরাসরি দুর্ভিক্ষ চাপিয়ে দেয়ার পেছনে সবচেয়ে বড় কারণ হলো—আঞ্চলিক ইচ্ছাশক্তির অভাব। আরব ও ইসলামি বিশ্বে ইসরায়েলের নিরঙ্কুশ আধিপত্য মোকাবিলার কোনও কার্যকর উদ্যোগ দেখা যায়নি। এটি শুধু গাজার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, ইসরায়েল সরাসরি লেবানন ও সিরিয়ায়ও আগ্রাসন চালাচ্ছে। পাশাপাশি, পশ্চিম তীরকে বসবাসের অযোগ্য করে তুলতেও নানামুখী নীতি জারি রেখেছে।
ফলে, গাজায় দীর্ঘ সময় ধরে চলা এই গণহত্যার অনুমতি দিয়ে ইসরায়েল এখন নিজেকে একটি আধা-সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ পেয়েছে। অথচ এই ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞও আঞ্চলিক শক্তিগুলোকে—বিশেষ করে ফিলিস্তিন-সংলগ্ন আরব রাষ্ট্র, উপসাগরীয় দেশগুলো এবং তুরস্ককে—কোনো কার্যকর প্রতিরোধে বাধ্য করতে পারেনি। দুর্ভিক্ষের মতো ভয়ংকর পদক্ষেপেও তারা সক্রিয় হয়নি। এমনকি ইসরায়েলের আগ্রাসন ফিলিস্তিনের সীমা পেরিয়ে লেবানন ও সিরিয়ায় পৌঁছালেও তারা কোনো সমন্বিত আঞ্চলিক নীতি গ্রহণ করেনি। সংকীর্ণ রাষ্ট্রিক স্বার্থেই তারা আবদ্ধ থেকেছে, এবং বৃহত্তর ইসরায়েলি হুমকিকে উপেক্ষা করে চলেছে।
কীভাবে দুর্ভিক্ষ বন্ধ করা যাবে?
যখন আরব ও মুসলিম দেশগুলোর কথা বলা হয়, তখন রিয়াদে অনুষ্ঠিত আরব-ইসলামি যৌথ সম্মেলনের সিদ্ধান্তগুলো স্মরণ করতেই হয়। ২০২৩ সালের ১১ নভেম্বরের সেই সম্মেলনের চূড়ান্ত ঘোষণায় স্পষ্টভাবে বলা হয়েছিল—‘গাজায় জরুরি, টেকসই ও পর্যাপ্ত মানবিক সহায়তা প্রবেশ নিশ্চিত করতে হবে।’ পরের বছর একই রকম আরেকটি সম্মেলনেও পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তগুলোরই পুনরুল্লেখ করা হয়। অথচ বাস্তবে সেই সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়ন হয়নি—বরং প্রশ্ন জেগেছে, আরব-মুসলিম দেশগুলো কি এমন সব সিদ্ধান্ত নিচ্ছিল, যেগুলো বাস্তবায়নে তারা অক্ষম? নাকি এসব ছিল লোক দেখানো বক্তব্য, যেগুলোর কোনো বাস্তব ফল নেই?
আজ আর বলার অপেক্ষা রাখে না—ইসরায়েলের নির্বিচার গণহত্যা ও পরিকল্পিত দুর্ভিক্ষ জিইয়ে রাখার অন্যতম কারণ হলো আরব বিশ্বের নিষ্ক্রিয়তা। এই নিষ্ক্রিয়তার কারণ যা-ই হোক—গণহত্যার সময়েও সম্পর্ক স্বাভাবিক রাখা, প্রতিরোধ আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালানো, কিংবা আরব জনগণের বিক্ষোভ ও সহমর্মিতার প্রকাশ ঠেকিয়ে রাখা। এমনকি যেসব মানুষ অন্তত নৈতিকভাবে ফিলিস্তিনিদের পাশে দাঁড়াতে চায়, তাদের জন্যও পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।
এ অবস্থায় স্পষ্ট, সমস্যার কেন্দ্রবিন্দু শুধুমাত্র সহায়তা পাঠানো নয় বরং প্রথম সমস্যা—এই সহায়তা গাজায় প্রবেশ করতে না পারা। দ্বিতীয়ত, গণহত্যা থামানোর মতো কোনো বাস্তব পদক্ষেপ নেই। তৃতীয়ত, যেসব প্রতিরোধযোদ্ধা অবরোধ, আক্রমণ ও আন্তর্জাতিক উপেক্ষার মধ্যে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন—তাদের জন্য নেই কোনো রক্ষাকবচ, নেই কোনো ন্যায়সঙ্গত সমর্থন। কেউ তাদের রাজনৈতিক দর্শন বা কৌশলের সঙ্গে একমত না-ও হতে পারেন, কিন্তু এই ভিন্নমতের অজুহাতে গোটা গাজা উপত্যকাকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে দেওয়া—প্রকৃতপক্ষে পুরো আরব বিশ্বকেই মর্যাদাহীন করে দিচ্ছে। ইসরায়েল এই সুযোগেই পুরো অঞ্চলে নিজের আধিপত্য আরও জোরালো করছে।
এই প্রেক্ষাপটে সমাধানও আসতে হবে আরবদের ভেতর থেকেই। বিশেষত যখন গাজার সীমান্তে—মিশরের পাশে—বিপুল পরিমাণ ত্রাণবাহী ট্রাক আটকে আছে, তখন দরকার একটি সমন্বিত আরব-মুসলিম উদ্যোগ, যেটি সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে কার্যকর চাপ তৈরি করতে পারে। ইসরায়েল এতটা বেপরোয়া নয় যে, সে নিজে থেকেই সব আরব মিত্রদের সঙ্গে সম্পর্ক কে ঝুঁকিতে ফেলবে। আর যদি আরব ও মুসলিম বিশ্ব একত্রে ঘোষণা করে—মানবিক সহায়তা গাজায় জোরপূর্বক প্রবেশ করানো হবে—তাহলে ইসরায়েলের পক্ষেও সেই সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করা সহজ হবে না।
আরব সরকারগুলো চাইলে অন্তত একটি কাজ করতে পারে—নিজেদের জনগণকে প্রতিবাদের সুযোগ করে দিতে পারে। তারা যদি দুর্ভিক্ষ ও গণহত্যার বিরুদ্ধে নিজেদের ক্ষোভ প্রকাশ করতে পারে, ফিলিস্তিনিদের প্রতি সহমর্মিতা দেখাতে পারে—তাহলে তা সরকারগুলোকেও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে কিছুটা কৌশলগত সুবিধা দেবে। এমনকি যুক্তরাষ্ট্রকেও বাধ্য করতে পারে এই মানবিক সংকটের ইতি টানতে।
সুতরাং সমাধান শুধু সাহায্যের নয়, এর চেয়েও বড় কথা—সাহায্যের রাস্তা খোলা, গণহত্যা রোধ এবং ফিলিস্তিনিদের প্রতিরোধ সংগ্রামকে পেছন থেকে অন্তত ন্যায়ভিত্তিক সমর্থন দেওয়া। এই তিনটিই এখন জরুরি।
সূত্র: আল জাজিরা