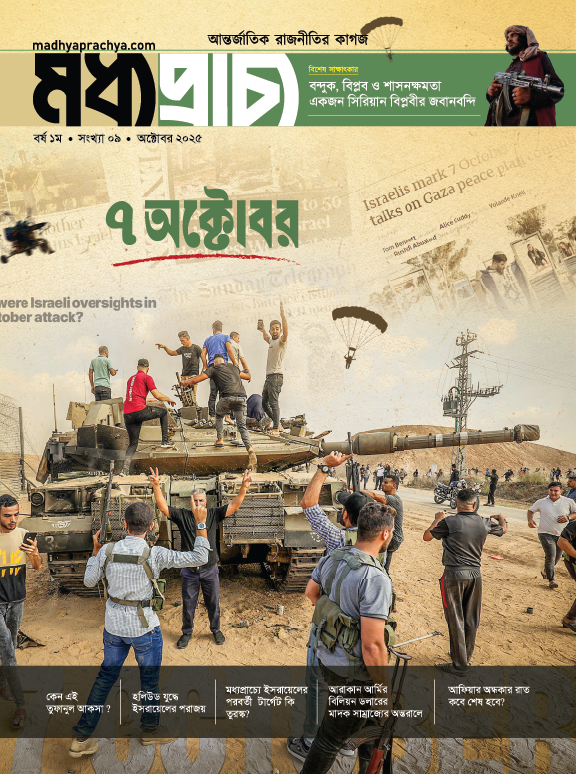২০২০ সালের ডিসেম্বর। ভারতের উত্তর প্রদেশে বন্ধুদের বাড়ির পাশে গ্রামের রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল ১৬ বছরের মোহাম্মদ সাকিব। সেখান থেকেই একদল লোক তাকে টেনে নিয়ে গিয়ে মারধর করে।
কয়েক ঘণ্টা পর সাকিব নিজেকে দেখতে পান থানার হাজতে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ—ভারতের সবচেয়ে বিতর্কিত ও রাজনৈতিকভাবে স্পর্শকাতর অপরাধগুলোর একটি, ‘লাভ জিহাদ’। অভিযোগ, হিন্দু মেয়েদের প্রেমের ফাঁদে ফেলে ধর্মান্তরিত করার ষড়যন্ত্রে যুক্ত মুসলিম তরুণদের একজন হলেন তিনি।
টিআরটি ওয়ার্ল্ডকে সাকিব বলেন, ‘আমি এক বন্ধুর সঙ্গে জন্মদিনের দাওয়াত থেকে ফিরছিলাম। তখন দেখি কয়েকজন ছেলে রাস্তায় এক মেয়েকে থামিয়েছে।’
‘আমি জানতে চাইলাম কী হচ্ছে। ওরা হঠাৎ করেই আমার ওপর হামলা করে বসে—কোনো কারণ ছাড়াই। পরে পুলিশ আসে এবং আমাকে থানায় নিয়ে যায়। অথচ মেয়েটি সোজাসুজি বলে দেয়, আমি তার সঙ্গে ছিলাম না। তবু তারা আমার বিরুদ্ধেই মামলা করে।’
সাকিব এখন ২০ বছর বয়সী। প্রায় চার বছরের আইনি লড়াই। ৭০টির বেশি আদালত শুনানি এবং ছয় মাস জেল খাটার পর সম্প্রতি তিনি খালাস পান।
তার আইনজীবী বলেন, উত্তর প্রদেশে ‘লাভ জিহাদ আইন’ অনুযায়ী এটিই প্রথম মামলা যেখানে কেউ পুরোপুরি খালাস পেলেন।
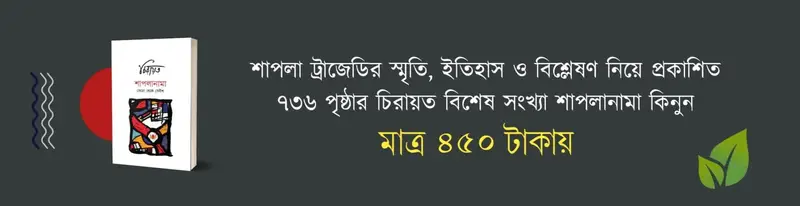
২০২০ সালে উত্তর প্রদেশে চালু হয় ‘অবৈধ ধর্মান্তর আইন’। এই আইনে বলা হয়েছে, বিয়ের মাধ্যমে, জোর করে কিংবা প্রতারণা করে ধর্মান্তর ঘটানো অপরাধ। তবে আইনটি নিয়ে শুরু থেকেই তীব্র বিতর্ক রয়েছে। সমালোচকদের অভিযোগ, এই আইনকে ব্যবহার করা হচ্ছে মুসলিম যুবকদের হয়রানি করতে।
জাতীয় পর্যায়ে এ ধরনের মামলার নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান না থাকলেও অধিকারকর্মীরা বলছেন, এর সংখ্যা হাজার ছাড়িয়ে যেতে পারে।
শুধু উত্তর প্রদেশেই ২০২৪ সালের জুলাই পর্যন্ত এ আইনে ৮৩৫টি মামলা হয়েছে, গ্রেপ্তার করা হয়েছে ১ হাজার ৬৮২ জনকে।
অথচ এসব মামলায় এখনো পর্যন্ত কারও দোষ প্রমাণিত হয়নি। ২০২৪ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত একটি মামলাতেও দোষী সাব্যস্ত হওয়ার নজির নেই—তবু শত শত মামলা এখনো চলছে আদালতে।
ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষার নামে এই আইন এখন ব্যবহৃত হচ্ছে আন্তধর্ম সম্পর্ক, বিশেষ করে মুসলিম পুরুষ ও হিন্দু নারীর সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার হিসেবে।
আইনটি কার্যকরের মাত্র ১৮ দিন পরই সাকিবের বিরুদ্ধে মামলা হয়। তিনিই ছিলেন ‘লাভ জিহাদ’ আইন অনুযায়ী প্রথম দিককার অভিযুক্তদের একজন।
পরে একই ধরনের আইন চালু হয়েছে বিজেপি শাসিত আরও কয়েকটি রাজ্যে—এর মধ্যে রয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নিজ রাজ্য গুজরাটও। মানবাধিকারকর্মীদের অভিযোগ, এভাবেই ধীরে ধীরে একটি বৈষম্যমূলক আইনি কাঠামো গড়ে উঠছে, যা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পরিপন্থী এবং সাম্প্রদায়িক বিভাজনকে উসকে দিচ্ছে।
সাকিবের অভিজ্ঞতা ব্যতিক্রম কোন ঘটনা নয়।
২০২০ সালে উত্তর প্রদেশে আন্তধর্ম সম্পর্ককে লক্ষ্য করে কঠোর ‘ধর্মান্তর বিরোধী আইন’ চালুর পর থেকে শত শত মুসলিম যুবককে এই আইনে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
উত্তর প্রদেশেই বাস করেন ভারতের যেকোনো রাজ্যের মধ্যে সর্বাধিক মুসলিম—প্রায় ৩ কোটি ৮৫ লাখ। যা রাজ্যের মোট জনসংখ্যার প্রায় ২০ শতাংশ।
মিথ্যা মামলা
২০২০ সালে আইনটি চালু হওয়ার পর থেকে ২০২৪ সালের জুলাই পর্যন্ত উত্তর প্রদেশে ধর্মান্তরবিরোধী আইনে ৮৩৫টি মামলা রুজু হয়েছে, গ্রেপ্তার করা হয়েছে ১ হাজার ৬৮২ জনকে।
তবে এত বিপুল সংখ্যক মামলার পরও দণ্ডপ্রাপ্তির সংখ্যা হাতেগোনা। অনেক অভিযুক্তকে প্রমাণ ছাড়াই মাসের পর মাস, এমনকি বছরের পর বছর কাটাতে হয়েছে জেলে—বিচার শুরুর আগেই।
আইন বিশেষজ্ঞ ও অধিকারকর্মীদের অভিযোগ, নৈতিকতা ও জাতীয় পরিচয়ের নামে ভারতের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় সংখ্যালঘু মুসলিমদের টার্গেট করতেই ব্যবহার করা হচ্ছে এই আইন।
‘এই আইনে দায়ের হওয়া অধিকাংশ মামলাই ভুয়া,’ বলেন সাকিবের আইনজীবী মাশরুফ কামাল। ‘কাগজে-কলমে আইনটি ধর্মনিরপেক্ষ মনে হলেও বাস্তবে এটি প্রায় একচেটিয়াভাবে মুসলিমদের লক্ষ্য করেই করা।’
সাকিব বলেন, যাকে ঘিরে এই মামলা, সেই মেয়েটিকে তিনি চিনতেনই না; তাদের মধ্যে কোনো প্রেমের সম্পর্কও ছিল না। আদালতের নথি ও সাক্ষ্যপ্রমাণেও তার বক্তব্যের মিল পাওয়া যায়। এমনকি মেয়েটি নিজেও জেরা চলাকালে আদালতে বলেন, তিনি সাকিবকে চিনতেন না।
‘আদালতে মেয়েটি স্পষ্টভাবে বলেছে, সাকিবকে সে চেনে না,’ বলেন আইনজীবী কামাল। ‘প্রথমে সে বলেছিল, বন্ধুর বাড়ি গিয়েছিল। পরে চাপ দিয়ে সাকিবের নাম বলানো হয়।’
কামাল জানান, প্রথমে সাকিবকে ভুলে চোর ভেবে আটকানো হয়। সেই এলাকায় গাড়ি চুরির ঘটনা বেড়ে যাওয়ায় সন্দেহ ছিল। মারধরকারী গ্রুপের মধ্যে মুসলিমরাও ছিলেন। তবে পুলিশ এসে জানতে পারে মেয়েটি হিন্দু সম্প্রদায়ের, তখন ঘটনাটির বর্ণনা পাল্টে যায়।
‘দায় এড়াতে ঘটনাকে সাম্প্রদায়িক রঙ দেওয়া হয়েছে,’ বলেন কামাল। ‘তারপর অপহরণ, জোরপূর্বক বিয়ে করানোর উদ্দেশ্যে প্রেমজাল ফাঁদা এবং নারীর সম্মান লঙ্ঘনের অভিযোগ আনা হয়।’
সাকিবের বাবা আগেই মারা গেছেন। সংসার এমনিতেই ছিল টানাপোড়েনের মধ্যে। এর মধ্যেই মামলার খরচ, যাতায়াত ও আইনজীবীর ফি মেটাতে পরিবারকে হাজার হাজার রুপি খরচ করতে হয়েছে।
‘এখন আমি ওয়েল্ডারের কাজ করি,’ বলেন সাকিব। ‘সব খরচ আমার ভাইকে বহন করতে হয়েছে। সপ্তাহে দুই-তিন দিন আমাদের কোর্টে যেতে হতো। খুব ক্লান্তিকর ছিল।’
সাকিব তখন অপ্রাপ্তবয়স্ক হলেও তাকে প্রাপ্তবয়স্ক হিসেবে বিচার করা হয়। তার আইনজীবী কামাল বলেন, ‘শুরুর দিকে আমরা তার বয়স প্রমাণ করতে পারিনি, কারণ তার কোনো স্কুল সার্টিফিকেট ছিল না। পরে অবশ্য জন্মসনদ জোগাড় করতে পেরেছিলাম।’
কয়েকটি ঘটনায় প্রাথমিক তদন্তের পর উত্তর প্রদেশ পুলিশকে মামলার অভিযোগ তুলে নিতে হয়েছে। কারণ, তদন্তে দেখা গেছে—এসব মামলা অতিরঞ্জিত ও ভিত্তিহীন।
এই বিষয়ে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট রাজ্য পুলিশের ভূমিকার কড়া সমালোচনা করেছে। আদালত বলেছে, ধর্মান্তরবিরোধী আইন পক্ষপাতমূলকভাবে এবং অনুচিতভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।
২০২৫ সালের মার্চে তৎকালীন প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্নার নেতৃত্বে গঠিত একটি বেঞ্চ, একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন মামলায় এই আইন প্রয়োগের জন্য উত্তর প্রদেশ সরকারকে প্রকাশ্যে ভর্ৎসনা করে।
রাজনৈতিক প্রচারণা থেকেই উঠে
এসেছে এই আইন
ভারতে ‘লাভ জিহাদ’ শব্দটি প্রথম আলোচনায় আসে ২০০০-এর দশকের শেষ দিকে। ডানপন্থী হিন্দু গোষ্ঠীগুলো এটি জনপ্রিয় করে তোলে, পরে তা আরও জোরালোভাবে তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) নেতারা। ২০১৪ সাল থেকে দলটি কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনা করছে।
এই অভিযোগের ভিত্তি একটি প্রমাণহীন দাবি—মুসলিম পুরুষরা পরিকল্পিতভাবে হিন্দু নারীদের প্রেমে ফেলে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করছেন, যার মাধ্যমে ভারতের হিন্দু জনসংখ্যার ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে।
তত্ত্বটির পক্ষে কোনো বাস্তব তথ্য-প্রমাণ না থাকলেও, ভারতের কয়েকটি রাজ্যে ধর্মান্তরবিরোধী আইন পাস করা হয়েছে, যেগুলো কার্যত ধর্মান্তরের মাধ্যমে আন্তধর্মীয় বিয়েকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করে।
এই আইন অনুযায়ী ধর্মান্তরের আগে কর্তৃপক্ষকে আগাম জানাতে হয়, এমনকি পারিবারিক সদস্যদের আদালতে গিয়ে বিয়ের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করার সুযোগও রাখা হয়েছে। সমালোচকদের মতে, এতে প্রাপ্তবয়স্কদের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হচ্ছে।
তাঁদের মতে, ‘লাভ জিহাদ’ ঘিরে যে আইনি কাঠামো তৈরি হচ্ছে, তা শুধু কিছু চরমপন্থী গোষ্ঠীর মতাদর্শের ফসল নয়; বরং এটি একটি বৃহত্তর রাষ্ট্রীয় প্রকল্পের অংশ, যার পেছনে সরকারি মদদ রয়েছে।
দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও বর্তমান সরকারের সমালোচক আপূর্বানন্দ ঝা বলেন, ‘সরকারি কর্মকর্তারা—এমনকি মুখ্যমন্ত্রীরাও—খোলাখুলিভাবেই ‘লাভ জিহাদ’ ষড়যন্ত্র তত্ত্বকে সমর্থন করে বক্তব্য দিয়েছেন।’
‘এই আইনগুলো আসলে কারও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে নয়, বরং মুসলিমদের সামাজিক কোনঠাসা করতে তৈরি’ বলেন একাধিক বিশ্লেষক।
হিউম্যান রাইটস ওয়াচসহ বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থা সতর্ক করে বলেছে, এসব আইন ও ঘৃণামূলক বক্তব্য বৃদ্ধির মাধ্যমে ভারতে এক ধরনের রাষ্ট্রীয় মদদপুষ্ট অসহিষ্ণুতা তৈরি হচ্ছে।
২০২৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতা কমিশন (USCIRF) আবারও ভারতকে ‘বিশেষ উদ্বেগের দেশ’ হিসেবে তালিকাভুক্ত করে। কমিশন জানায়, ধর্মীয় সংখ্যালঘু—বিশেষ করে মুসলিমদের বিরুদ্ধে সহিংসতা ও বৈষম্য উসকে দিতে সরকারি কর্মকর্তারাই ভূমিকা রাখছেন।
সাকিবের খালাস মুসলিম সম্প্রদায়ের কাছে আশার আলো হয়ে উঠলেও, ধর্মান্তরবিরোধী আইনে নতুন নতুন মামলা দায়েরের ঢেউ ঠেকাতে তা খুব একটা প্রভাব ফেলছে না।
মানবাধিকার সংগঠনগুলোর মতে, এসব আইন সমভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে না। বাস্তবিক জোর-জবরদস্তির ঘটনা মোকাবিলার চেয়ে বরং মুসলিমদের টার্গেট করতেই এগুলো ব্যবহার করা হচ্ছে।
২০২৫ সালের এপ্রিল মাসে ‘সিটিজেনস ফর জাস্টিস অ্যান্ড পিস’ নামের একটি সংগঠন সুপ্রিম কোর্টে দায়ের করা এক আবেদনে জানায়—উত্তর প্রদেশের আইনটি ‘অস্ত্র’ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে আন্তধর্মীয় দম্পতিদের হয়রানি করতে। এসব মামলার বেশিরভাগই দায়ের করেছে তৃতীয় পক্ষ—অর্থাৎ স্বয়ং নারীরা নয়, বরং বাইরের লোকজন। টার্গেট করা হয়েছে মূলত হিন্দু নারী ও মুসলিম পুরুষের সম্পর্ককে।
‘পুলিশ এমনভাবে আচরণ করে, যেন নারীর সম্মতির কোনো মূল্যই নেই,’ বলেন অধ্যাপক আপূর্বানন্দ। ‘এটা এক ধরনের সামন্তবাদী মানসিকতা এবং রাজনৈতিক কৌশল। এই আইন ন্যায়বিচারের জন্য নয়, বরং নিয়ন্ত্রণের জন্য।’
বহু ক্ষেত্রে দেখা গেছে, মুসলিম পুরুষকে স্বেচ্ছায় বিয়ে করা হিন্দু নারীদের কথা বিশ্বাসই করা হয় না। বরং তাদের জোর করে বিয়ে করা হয়েছে—এমনভাবেই উপস্থাপন করা হয়। কিছু ঘটনায় আদালতের সুরক্ষা সত্ত্বেও দম্পতির বাড়িঘর ভেঙে ফেলা হয়েছে, পরিবারের সদস্যদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
২০২৪ সালে উত্তর প্রদেশে এক মুসলিম পরিবারের ছয়টি বাড়ি গুঁড়িয়ে দেয় স্থানীয় কর্তৃপক্ষ। অভিযোগ ছিল, পরিবারের একজন পুরুষ এক হিন্দু নারীকে অপহরণ করেছে। অথচ সেই নারী আদালতে স্বীকার করেছিলেন, তিনি স্বেচ্ছায় গিয়েছিলেন।
আপূর্বানন্দ বলেন, ‘এটা নীরবতা নয়, এটা পরিকল্পিত নিপীড়ন।’
‘লাভ জিহাদ আইন’-এর অপব্যবহার
ভারতের বিজেপির ঘনিষ্ঠ কট্টর হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলো—যেমন বজরং দল ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদ—তথাকথিত ‘লাভ জিহাদ’-এর অভিযোগে হামলা ও হয়রানির ঘটনায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।
তাদের সদস্যরা কখনো কখনো প্রকাশ্য স্থান, জিম কিংবা কোচিং সেন্টারে গিয়ে মুসলিম কর্মীদের বের করে দেওয়ার চেষ্টা চালায়। অভিযোগ, এসব জায়গায় হিন্দু নারীদের নিরাপত্তা হুমকির মুখে।
আরও কিছু ঘটনায় দেখা গেছে, এসব সংগঠনের কর্মীরা জন্মদিনের মতো ব্যক্তিগত আয়োজন চলা অ্যাপার্টমেন্টে জোর করে ঢুকে পড়েছে, সেখানে থাকা মুসলিম তরুণদের হেনস্তা করেছে। এমনকি সেই দৃশ্যের ভিডিও তুলে সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়েছে—লজ্জা দেওয়ার উদ্দেশ্যে।
এইভাবে ‘লাভ জিহাদ’ আইনকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ও ধর্মীয় বিদ্বেষ ছড়াতে ব্যবহার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে।
এই ধরনের নজরদারি ও হামলার ঘটনা শুধু উত্তর ভারতের হিন্দুত্ববাদী রাজ্যগুলোতেই সীমাবদ্ধ নয়। এখন এটি গোটা দেশজুড়েই ছড়িয়ে পড়ছে—রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট ভিন্ন এমন এলাকাতেও একইভাবে দেখা যাচ্ছে হয়রানি, নজরদারি ও মোরাল পুলিশিংয়ের প্রবণতা।
গত মাসেই ভারতের পূর্ব প্রান্তের রাজ্য আসামে—চীন ও মিয়ানমারের সীমান্তবর্তী অঞ্চল—এক মুসলিম তরুণকে তথাকথিত ‘লাভ জিহাদ’-এর অভিযোগে প্রকাশ্যে মারধর করে একটি উগ্র গোষ্ঠী। ধারণা করা হচ্ছে, হামলাকারীরা বজরং দল বা বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মতো কট্টর সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। ওই হামলার দৃশ্য সরাসরি সম্প্রচারও করা হয়।
পরবর্তীতে পুলিশ পর্যবেক্ষকেরাও স্বীকার করেন, এটি ছিল অবৈধ ‘নৈতিক পুলিশিং’-এর ঘটনা।
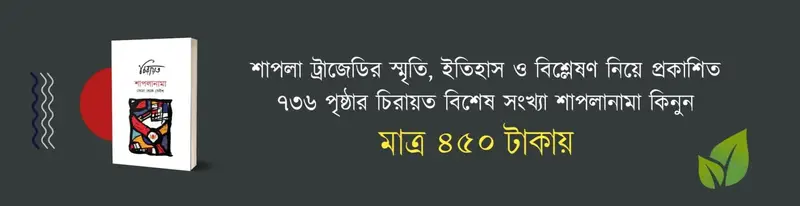
প্রতিবেদনগুলো বলছে, এ ধরনের মামলার প্রায় ৬০ শতাংশই দায়ের করে তৃতীয় পক্ষ—মূলত হিন্দুত্ববাদী কর্মীরা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট নারী বা তাঁর পরিবার এসব মামলার বাদী নন।
ডানপন্থী এসব দলের কর্মীরা নিজেদের ‘হিন্দু নারীদের অভিভাবক’ হিসেবে দাবি করে থাকেন। তাঁরা স্থানীয় নেটওয়ার্ক ও হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের মাধ্যমে সংগঠিত হয়ে আন্তঃধর্মীয় মেলামেশার ওপর নজরদারি চালান এবং যখন-তখন হস্তক্ষেপ করেন।
এই প্রবণতা ক্রমেই ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন অধিকারকর্মীরা।
অনেক ক্ষেত্রেই এই হিন্দুত্ববাদী কর্মীরা প্রকাশ্যে প্রেমিক যুগলদের মুখোমুখি হন, পরিবারের সদস্যদের ওপর চাপ সৃষ্টি করে অভিযোগ দায়ের করান এবং ব্যক্তিগত তথ্য অনলাইনে ছড়িয়ে সামাজিক চাপ তৈরি করেন।
এই তৃণমূল পর্যায়ের সংগঠিত প্রচেষ্টা পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে—এমনকি যখন সংশ্লিষ্ট নারী স্পষ্টভাবে বলে দেন, তাঁর ওপর কোনো জোরজবরদস্তি বা অপরাধমূলক কিছু ঘটেনি।
তবে সাকিবের মতো যাঁরা এ ধরনের অভিযোগের মুখে পড়েছেন, তাঁদের জন্য প্রভাবটা কেবল আদালত অবধি সীমাবদ্ধ থাকে না—তা ছড়িয়ে পড়ে তাঁদের দৈনন্দিন জীবনে।
‘আমি খুব ভয়ে থাকি। এখন আর কোনো মেয়ের কাছেও যাই না,’ বলেন সাকিব। ‘আমার অনেক হিন্দু বন্ধু আছে। কিন্তু এখন তাদের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখতে ভয় লাগে। আর কোনো ঝামেলায় পড়তে চাই না।’
সূত্র: ১৭/০৬/২০২৫ তারিখে টিআরটিতে প্রকাশিত নয়া দিল্লির তথ্যচিত্র নির্মাতা হানান জাফর ও ভারতের একজন মাল্টিমিডিয়া রিপোর্টার ড্যানিশ পণ্ডিত এর লেখা অবলম্বনে প্রস্তুতকৃত।