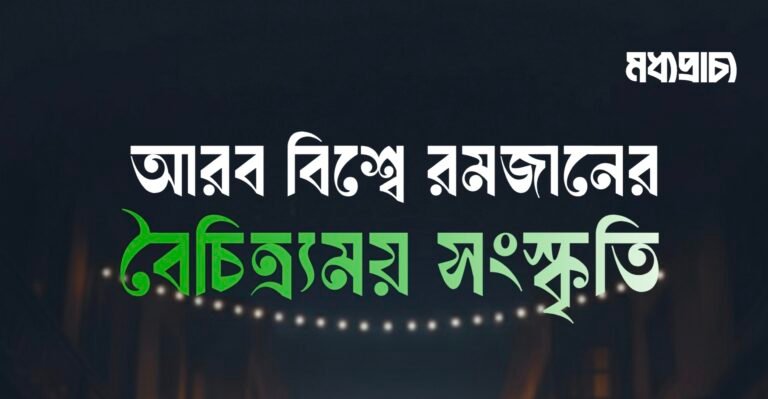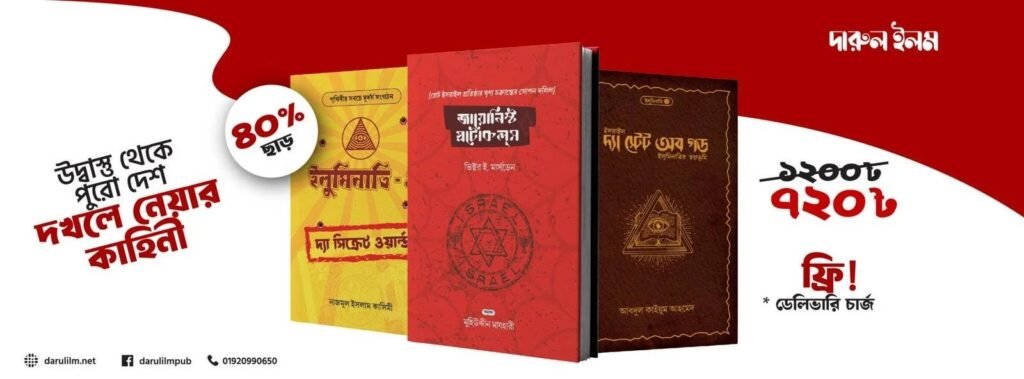সম্প্রতি কাশ্মীরের ভারত-দখলকৃত অংশে পুলওয়ামায় একটি হামলার ঘটনার জন্য পাকিস্তানকে দায়ী করে ভারত। এর জেরে দু’দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক খারাপ হয়, ভারত সিন্ধু নদীর পানি চুক্তি স্থগিত করে, আর দুই দেশ থেকেই আসে সামরিক হুমকি। এই সব ঘটনার ফলে সংকটের রূপ আরও জটিল হয়।
এখন বিষয়টা শুধু ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যকার কোনো সীমিত সংঘাত নয়—এটি হয়ে উঠেছে বৈশ্বিক নিরাপত্তার জন্যও হুমকি। কারণ উভয় দেশই পারমাণবিক শক্তিধর। এ ধরনের সংঘাত গোটা বিশ্বের রাজনীতিতে গভীর প্রভাব ফেলতে পারে।
এই সংকট এমন এক সময়ে সামনে এসেছে, যখন বিশ্বব্যবস্থা দ্রুত বদলে যাচ্ছে। একক নেতৃত্বাধীন (যেমন: যুক্তরাষ্ট্র) পৃথিবী থেকে আমরা এখন একটি বহুমেরুকেন্দ্রিক পৃথিবীর দিকে এগোচ্ছি, যেখানে চীন, রাশিয়া, এমনকি আঞ্চলিক শক্তিগুলোর ভূমিকাও ক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।
বিশ্বের বড় শক্তিগুলোর মধ্যে যেমন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে বাণিজ্য ও আধিপত্য বিস্তার নিয়ে প্রতিযোগিতা চলছে, তেমনি যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার মধ্যে সম্পর্কও রয়ে গেছে টানাপোড়েনপূর্ণ। এসব বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা অন্য দেশগুলোর কৌশলগত অবস্থান নির্ধারণে প্রভাব ফেলছে।
এই অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও রাশিয়া—এই তিন শক্তিই নিজেদের প্রভাব বাড়াতে চাইছে বিভিন্ন অঞ্চলের প্রভাবশালী দেশগুলোর সঙ্গে কৌশলগত সম্পর্ক গড়ে তুলে। দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত ও পাকিস্তান—উভয়ই তাদের নিজ নিজ মিত্র হিসেবে তুলে ধরতে চায় এই বৈশ্বিক শক্তিগুলো।
সব মিলিয়ে বোঝা যায়, ভারত-পাকিস্তান সংকট আসলে শুধু সীমান্ত বিরোধ নয়। এটি বৈশ্বিক শক্তির লড়াইয়ের একটি বড় ক্যানভাস, যেখানে প্রতিটি পদক্ষেপের প্রতিধ্বনি শোনা যায় সারা বিশ্বে।
বহুধ্রুববিশ্ব: এক পরিবর্তনশীল বাস্তবতা
বর্তমান বিশ্ব যে বহুধ্রুবব্যবস্থার দিকে এগোচ্ছে, তা আগের শীতল যুদ্ধের সময়কার অবস্থার চেয়ে একেবারেই ভিন্ন। তখনকার পৃথিবী ছিল মূলত দুটি মেরুতে বিভক্ত—যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন। এই বিভাজন ছিল কেবল রাজনৈতিক বা কৌশলগত নয়, বরং আদর্শগত ও ভৌগোলিকও ছিল।
কিন্তু একবিংশ শতাব্দীর বহুধ্রুববিশ্বে সেই রকম স্পষ্ট বিভাজন আর নেই। আজকের বিশ্বে ‘পূর্ব-পশ্চিম’, ‘উত্তর-দক্ষিণ’, ‘পশ্চিমা বিশ্ব বনাম অপশ্চিমা বিশ্ব’—এই ধারণাগুলো আর আগের মতো বাস্তবতা তুলে ধরে না। বরং আমরা এমন এক নতুন ব্যবস্থার মধ্যে আছি, যা এখনো পুরোপুরি গঠিত হয়নি, কিন্তু নানা টানাপড়েন ও জটিলতার মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে রূপ নিচ্ছে।
যদিও পুরনো আদর্শিক ব্লকগুলো এখন আর অস্তিত্ব রাখে না, আদর্শবাদ এখনও টিকে আছে। তবে তার প্রভাব এখন প্রশ্নবিদ্ধ। দেশগুলো এখন বাস্তবতানির্ভর কূটনীতির দিকে এগোচ্ছে, কারণ বর্তমান দুনিয়া অনেক বেশি জটিল, পারস্পরিকভাবে নির্ভরশীল এবং নানা দিকে খণ্ডিত।
ভবিষ্যতে নতুন শক্তিধর জোট বা জিওপলিটিকাল ব্লক গঠনে যেসব বিষয় মুখ্য ভূমিকা রাখবে তা হলো: অর্থনীতি, প্রযুক্তি, নিরাপত্তা, জনসংখ্যা, সংস্কৃতি ও সভ্যতা। এই উপাদানগুলো নতুন নতুন প্রতিযোগিতা, জোট এবং শক্তির ভারসাম্য সৃষ্টি করতে পারে।
আজকের বিশ্বে আর সেভাবে স্পষ্ট বিভক্তি নেই—না আদর্শে, না জোটে, না মেরুতে। উদাহরণস্বরূপ, ভিয়েতনাম এখন চীনের বিরুদ্ধে সামরিক সহযোগিতায় যুক্তরাষ্ট্রের পাশে রয়েছে, অথচ ইউক্রেন ইস্যুতে রাশিয়াকে সমর্থন দিচ্ছে। তুরস্কও একদিকে ইউক্রেনকে সমর্থন দিচ্ছে, আবার অন্যদিকে রাশিয়া-ইউক্রেনের মাঝে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকাও পালন করছে। এমনকি বিশ্বব্যাপী গুরুত্বপূর্ণ শস্যচুক্তির মতো উদ্যোগেও ভূমিকা নিচ্ছে।
এসব ঘটনাই দেখায়, আজকের বহুধ্রুববিশ্ব একেবারে আলাদা ধরণের, যা শীতল যুদ্ধের সময়কার দ্বিমেরুবিশ্ব থেকে অনেকটাই ভিন্ন।
বর্তমানে বিশ্বজুড়ে যে অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তাজনিত জটিলতা চলছে, সেটাকে একরকম ‘রূপান্তরের প্রসবব্যথা’ বলেই ধরা যায়—এক নতুন বিশ্বব্যবস্থায় উত্তরণের পূর্বলক্ষণ।
এই রূপান্তরপর্বের মধ্যেই নানা সংকট ও সঙ্ঘাত সৃষ্টি হচ্ছে। এর মধ্য দিয়েই নতুন শক্তির কেন্দ্র তৈরি হবে, নতুন ভারসাম্য গড়ে উঠবে। এমনকি ভারত-পাকিস্তানের মতো পুরনো শত্রুতা যদি বড় ধরনের সংঘাতে রূপ নেয়, সেটিও এই নতুন বহুধ্রুববিশ্বের কাঠামো গঠনে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারে।
এই সময়কে ঘিরে যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও রাশিয়ার মতো বিশ্বশক্তিগুলো নিঃসন্দেহে সতর্ক দৃষ্টিতে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে এবং প্রয়োজন হলে অবস্থানও নেবে। তবে অবস্থান নেওয়া মানেই সরাসরি যুদ্ধে জড়ানো নয়।
বহুধ্রুববিশ্বের দিকে অগ্রসরমান এই সময়ে, বিশ্বশক্তিগুলো এমন কোনো বড় যুদ্ধ চাইবে না, বিশেষ করে দুটি পারমাণবিক শক্তিধর দেশের মধ্যে। কারণ এমন যুদ্ধের ফলাফল কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারে না, এবং তা যেকোনো সময় সব পক্ষের জন্যই বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। এমন এক অনিশ্চিত বিশ্বে, যুদ্ধ আর আগের মতো কোনো পক্ষের একক লাভের ক্ষেত্র নয়।
বিশ্বশক্তিগুলোর অবস্থান
ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সঙ্কট শুরু হওয়ার পর, যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও রাশিয়া উত্তেজনা না বাড়ানোর আহ্বান জানিয়েছে এবং শান্তিপূর্ণ আলোচনার ওপর জোর দিয়েছে।
এই তিনটি দেশের—যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও রাশিয়া—ভারত ও পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে বৈশ্বিক শক্তির ভারসাম্য এবং বহু-মেরুকেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থার বাস্তবতা অনুযায়ী। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যপথ, অর্থনৈতিক স্বার্থ, প্রযুক্তি নিয়ে চলমান প্রতিযোগিতা—এই সবকিছুই নির্ধারণ করে কে কাকে কিভাবে সমর্থন করবে।
যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গি
যুক্তরাষ্ট্র চীনকে এখন সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে, বিশেষ করে বাণিজ্যযুদ্ধে। ট্রাম্পের প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর এই যুদ্ধ আবারও তীব্র হয়েছে। তিনি বিভিন্ন দেশের ওপর নানা হারে শুল্ক আরোপ করেন। তবে এর মাঝেই যুক্তরাষ্ট্র ও তার বাণিজ্য অংশীদারদের মধ্যে শুল্ক নিয়ে আলোচনার অগ্রগতি নিয়ে কিছুটা আশাবাদ দেখা যায়।
এশিয়ায় যখন চীন ও জাপানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক কিছুটা জটিল, তখন ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়া যুক্তরাষ্ট্রের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এক কৌশল। মার্কিন অর্থমন্ত্রী স্কট বিসেন্ট জানিয়েছিলেন, প্রথম যে বাণিজ্য চুক্তিগুলো হবে, তার একটি ভারতের সঙ্গে হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
যুক্তরাষ্ট্র চায়, তার সরবরাহব্যবস্থা যেন শুধু একটি দেশের ওপর নির্ভরশীল না থাকে। তাই অনেক মার্কিন কোম্পানি এখন চীন ছেড়ে ভারতে বিনিয়োগ সরিয়ে নিচ্ছে।
তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, চীন যে বিশাল বাণিজ্যিক শূন্যতা তৈরি করবে, তা ভারত অল্প সময়ে পূরণ করতে পারবে না।
বাণিজ্যপথও এই প্রতিযোগিতায় বড় ভূমিকা রাখছে। চীনের ‘বেল্ট অ্যান্ড রোড’ প্রকল্পের পাল্টা হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র এখন ভারত-মধ্যপ্রাচ্য-ইউরোপ (IMEC) করিডোর প্রকল্পকে জোর দিয়ে সমর্থন করছে।
২০২০ সালে লাদাখে ভারত ও চীনা সেনাদের সংঘর্ষের সময় যুক্তরাষ্ট্র স্পষ্টভাবে ভারতের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিল।
এই কারণেই, যদিও ভারত ও পাকিস্তানের বর্তমান সঙ্কটে যুক্তরাষ্ট্র শান্তিপূর্ণ সমাধান চায়, তবুও চীনের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সে ভারতের সঙ্গেই থাকছে।
গণপ্রজাতন্ত্রী চীন
ভারতের উত্থান চীনকে স্পষ্টভাবে অস্বস্তিতে ফেলছে। কারণ, ভারত একদিকে যেমন বাণিজ্যে দারুণ অগ্রগতি করছে, তেমনি প্রযুক্তিখাতেও দ্রুত উন্নত হচ্ছে। পাশাপাশি, ভারত এখন বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক—দুই ক্ষেত্রেই নিজের অবস্থান শক্ত করছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো—ভারত যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলেছে এবং আন্তর্জাতিক সংকটগুলোর ক্ষেত্রে তারা একসঙ্গে কাজ করছে। এই বিষয়গুলো চীনের জন্য উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।
ব্রিকস (BRICS) জোট যখন প্রথম গঠিত হয়, তখন অনেকেই এটিকে পশ্চিমা বিশ্বের বিকল্প একটি শক্তি হিসেবে দেখেছিলেন। ভারত ও চীন উভয়ে যখন এই জোটের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, তখন ধারণা করা হয়েছিল—ভারত যেন আমেরিকার বিরুদ্ধে চীনের পাশে অবস্থান নিয়েছে।
কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্ট হয়ে গেছে, ব্রিকস আসলে পশ্চিমা-বিরোধী কোনো অর্থনৈতিক জোট নয়। কারণ, ২০২৪ সালের ১ জানুয়ারি মিশর, ইথিওপিয়া, ইরান, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং পরে সৌদি আরব এই জোটে যোগ দিয়েছে। ফলে চীন ও ভারতের একসঙ্গে ব্রিকসে থাকা মানেই নয়াদিল্লিকে পাকিস্তান ইস্যুতে সমর্থন করা—এমনটা ভাবার কোনো ভিত্তি নেই।
অন্যদিকে, পাকিস্তান চীনের ‘বেল্ট অ্যান্ড রোড’ প্রকল্পের অন্যতম প্রধান অংশীদার, যেখানে চীন বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছে।
ভারত-পাকিস্তান সংকটকে ঘিরে চীনের দেওয়া বক্তব্যে স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়—চীন ইসলামাবাদকেই সমর্থন করছে।
রুশ ফেডারেশন
সোভিয়েত যুগ থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত পাকিস্তান ও রাশিয়ার সম্পর্ক নানা চড়াই-উতরাইয়ের মধ্য দিয়ে চলেছে। আফগানিস্তানে সোভিয়েত আগ্রাসনের সময় পাকিস্তান সরাসরি মস্কোর বিরোধিতা করেছিল এবং সোভিয়েতবিরোধী যোদ্ধাদের অস্ত্র সরবরাহ করেছিল। তবে রাশিয়া আফগানিস্তান থেকে সরে যাওয়ার পর ধীরে ধীরে দুই দেশের সম্পর্ক উন্নতির দিকে যেতে থাকে। এমনকি ২০০৭ সালে রাশিয়া তালেবানের বিরুদ্ধে পাকিস্তানকে সহায়তা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।
বর্তমানে রাশিয়া ও চীনকে অনেকেই কৌশলগত মিত্র হিসেবে দেখছেন, যারা যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব মোকাবেলায় একসঙ্গে কাজ করছে। কিন্তু বাস্তবতা হলো—সোভিয়েত আমল থেকেই এই দুই পরাশক্তির মধ্যে এশিয়া জুড়ে প্রভাব বিস্তার নিয়ে প্রতিযোগিতা চলে আসছে।
চীন-রাশিয়া ঘনিষ্ঠতার পেছনে মূলত আমেরিকার আগ্রাসী নীতি কাজ করছে। তবে এটা ভাবা ভুল হবে যে, এই ঘনিষ্ঠতার ফলে তারা এশিয়ায় নিজেদের প্রতিযোগিতা ভুলে গেছে।
ইউক্রেন যুদ্ধের দিকে তাকালে দেখা যায়, রাশিয়ার ঘনিষ্ঠ মিত্র হওয়া সত্ত্বেও চীন এখনো এমন কোনো সামরিক বা কূটনৈতিক সহায়তা দেয়নি, যা মস্কোর পক্ষে যুদ্ধ জয় নিশ্চিত করতে পারে।
তাই চীন-রাশিয়া সম্পর্ককে সামনে রেখে ধরে নেওয়া উচিত হবে না যে, মস্কো পাকিস্তানের পাশে দাঁড়িয়ে ভারতের বিরুদ্ধে অবস্থান নেবে। কারণ রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সার্গেই লাভরভ সংকট নিরসনে কোনো একতরফা অবস্থান না নিয়ে বরং দুই দেশের মধ্যস্থতাকারী হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন।
এই সংকট থেকে চীন কি হারাবে?
নিঃসন্দেহে, ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সম্ভাব্য যুদ্ধের সবচেয়ে বড় ক্ষতিগ্রস্ত হবে চীন। কারণ চীন যেভাবে দুই দেশের সঙ্গে অর্থনৈতিক ভারসাম্য বজায় রেখে চলার চেষ্টা করছে, তা যুদ্ধ শুরু হলে ভেঙে পড়তে পারে। এতে শুধু তার বৈশ্বিক অবস্থান নষ্ট হবে না, চীনের বহু বছরের বিনিয়োগ ও স্বার্থ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।
শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের কথা বললেও, চীন সচরাচর আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বা সামরিক ইস্যুতে সরাসরি জড়ায় না। কারণ, এতে যেমন কিছু সুবিধা আছে, তেমনি রয়েছে বড় ঝুঁকিও। যুদ্ধ শুরু হলে চীনের ‘শান্তিপ্রিয়’ ভাবমূর্তি নষ্ট হতে পারে। তখন তাকে আর এমন এক শক্তি হিসেবে দেখা যাবে না, যে হিংস্র প্রতিযোগিতা ও আধিপত্যবাদী রাজনীতির বিরুদ্ধে।
তবে চীনের নিরপেক্ষ অবস্থান অনেক সময় এক পক্ষের জন্য সুবিধাজনক হয়ে দাঁড়ায়। বর্তমান পরিস্থিতিতে পাকিস্তানই এই নিরপেক্ষতার সুবিধা বেশি পাচ্ছে। যদিও চীন বালাকোট হামলার নিন্দা করেছে, তারা ভারতের দাবিকে সমর্থন করেনি বা পাকিস্তানকে দোষারোপ করেনি। বরং তারা পাকিস্তানের পক্ষ থেকে একটি দ্রুত ও নিরপেক্ষ তদন্তের আহ্বানকে সমর্থন জানিয়েছে।
কাশ্মীর ইস্যুতেও চীন সরাসরি জড়িয়ে আছে। কারণ কাশ্মীর শুধু ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বিভক্ত নয়—একাংশ রয়েছে চীনের অধীনেও। ১৯৬৩ সালে পাকিস্তান কাশ্মীরের একটি অংশ চীনের কাছে হস্তান্তর করে, যা ভারত কখনো মেনে নেয়নি। এই ঘটনা থেকেই চীন ও ভারতের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি হয়। সেই অভিজ্ঞতা এখন চীনকে ভারত-পাকিস্তান সংকটে মধ্যস্থতা করতে বাধা দিচ্ছে।
২০১৩ সালে প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং ‘বেল্ট অ্যান্ড রোড’ প্রকল্প ঘোষণা করেন, যার মূল স্তম্ভ হলো চীন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডর। এই করিডরের মাধ্যমে চীন সরাসরি গওয়াদার বন্দর হয়ে আরব সাগরে পৌঁছাতে পারে—যা কৌশলগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে এই করিডরের কিছু অংশ কাশ্মীর অঞ্চল দিয়ে যাওয়ায় ভারত এতে ক্ষুব্ধ।
চীন ও পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক ধীরে ধীরে সামরিক ও গোয়েন্দা সহযোগিতায় রূপ নিয়েছে। আজ চীন পাকিস্তানের সবচেয়ে বড় অস্ত্র সরবরাহকারী। দু’দেশের মধ্যে যৌথ সামরিক প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি বিনিময় ও গোয়েন্দা তথ্য আদান-প্রদানের মতো চুক্তিও হয়েছে। এ কারণে নয়াদিল্লি উদ্বিগ্ন।
চীনের এই অংশীদারিত্ব ইসলামাবাদের জন্য যেমন লাভজনক, তেমনি এটা নয়াদিল্লির উপর চাপ সৃষ্টির একটি কৌশল হিসেবেও কাজ করে। চীন চায় ভারতের আঞ্চলিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ন্ত্রণে রাখতে। তবে একটা মজার বিষয় হলো—একটি শক্তিশালী, স্থিতিশীল ভারত চীনের স্বার্থের পরিপন্থী নয়। ভারতের বাজারে চীনা পণ্যের চাহিদা অনেক, এবং বহু চীনা বিনিয়োগকারীও ভারতে সক্রিয়।
পরিস্থিতির পরিহাস হলো, যখন ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনা বাড়ছে, তখন চীন ও ভারতের সম্পর্ক ধীরে ধীরে উন্নতির পথে যাচ্ছিল। দুই দেশ সীমান্তে উত্তেজনা কমাতে, যৌথ টহল পুনরায় চালু করতে এবং সরাসরি ফ্লাইট চালুর বিষয়েও সম্মত হয়েছিল। কিন্তু কাশ্মীর ইস্যুতে সংঘর্ষ হলে এই ইতিবাচক ধারা থেমে যেতে পারে।
মোট কথা, চীন, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্ক জটিলভাবে জড়িয়ে আছে অর্থনীতি, সামরিক ও প্রযুক্তিগত বিভিন্ন খাতে। এই সম্পর্ক অনেক সূক্ষ্ম ভারসাম্যের উপর দাঁড়িয়ে, যেখানে প্রতিটি পদক্ষেপ আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক রাজনীতিকে প্রভাবিত করে। এই জটিল সম্পর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে আছে চীন। বহু বছরের বিনিয়োগ, পরিকল্পনা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে চীন যেসব সম্পর্ক গড়ে তুলেছে, একটি যুদ্ধ সেই সব অর্জন এক ঝটকায় ভেঙে দিতে পারে।
সূত্র: আল জাজিরা
এই লেখায় প্রকাশিত দৃষ্টিভঙ্গি লেখকের নিজস্ব। মধ্যপ্রাচ্যের সম্পাদকীয় নীতির সাথে মিল থাকা জরুরি নয়।